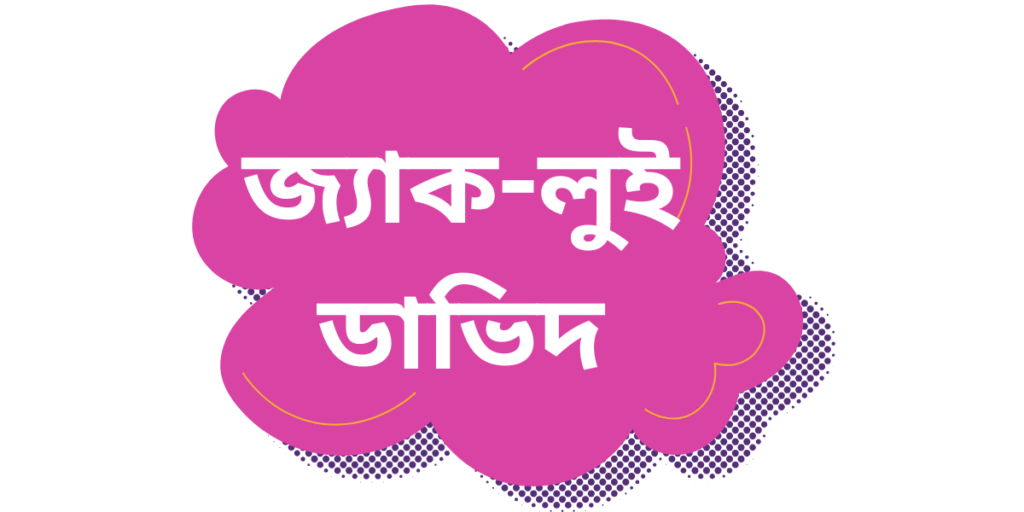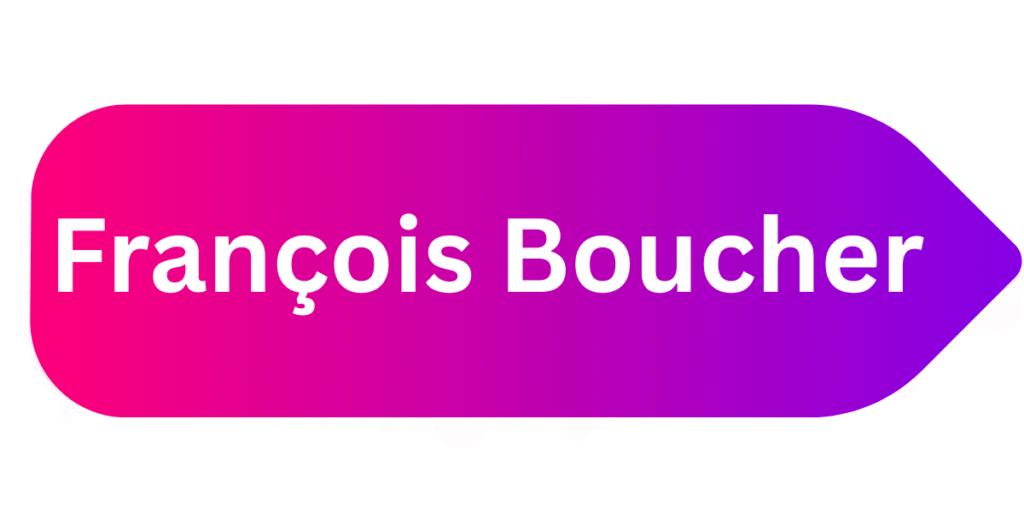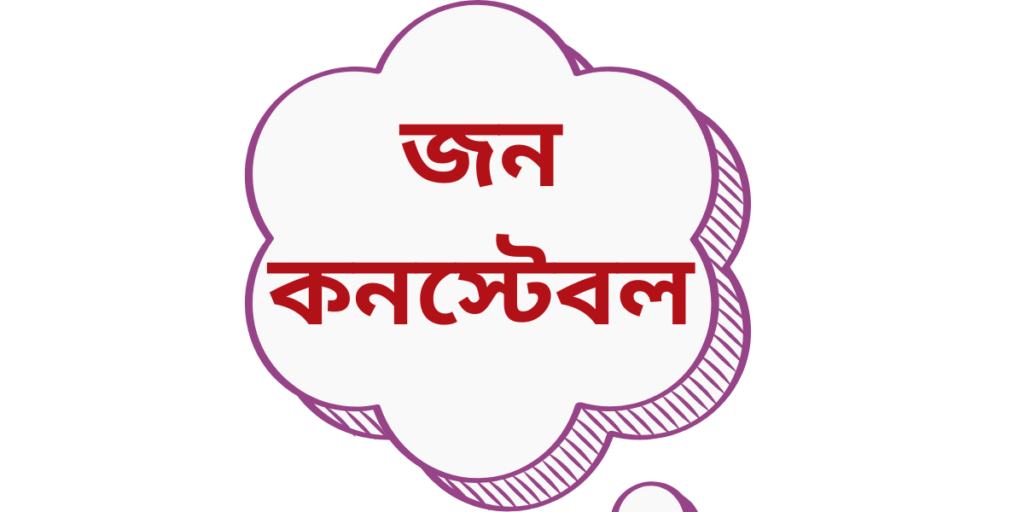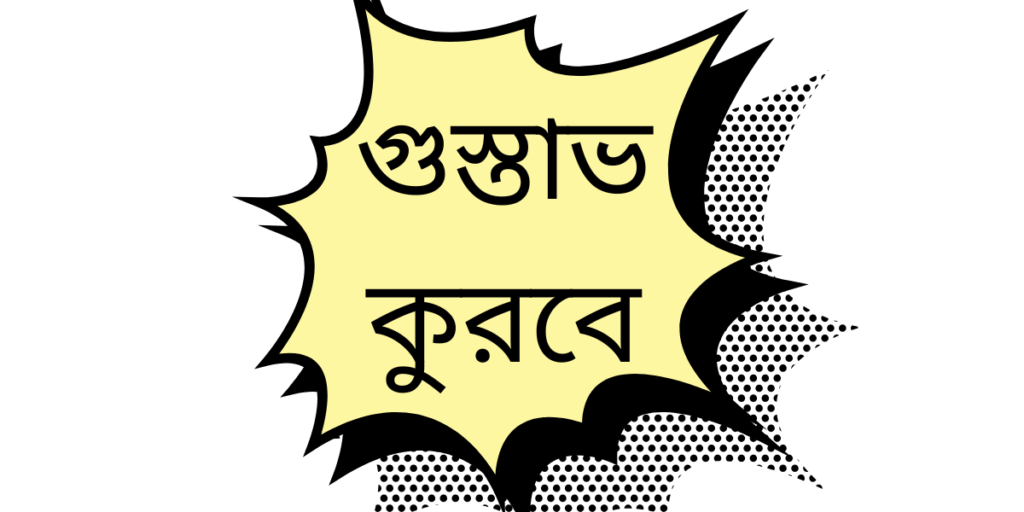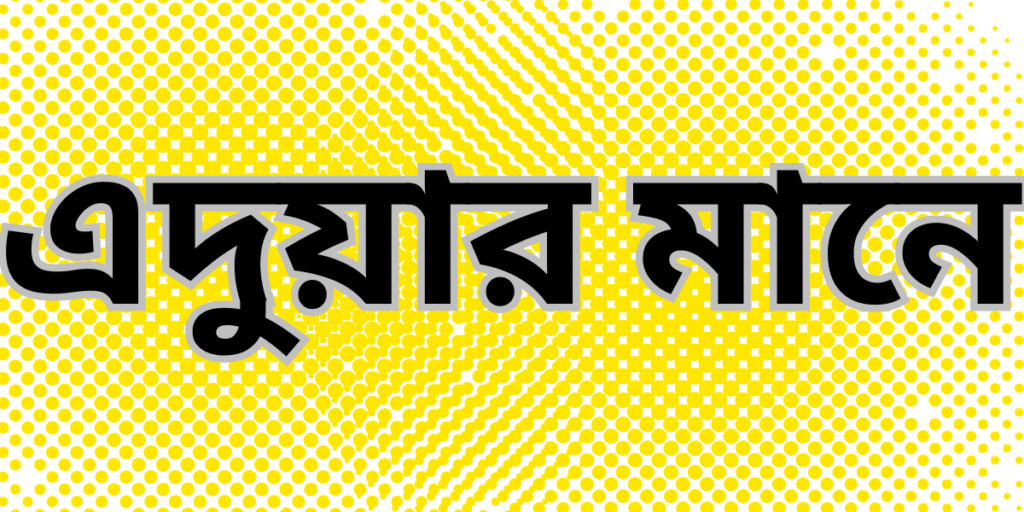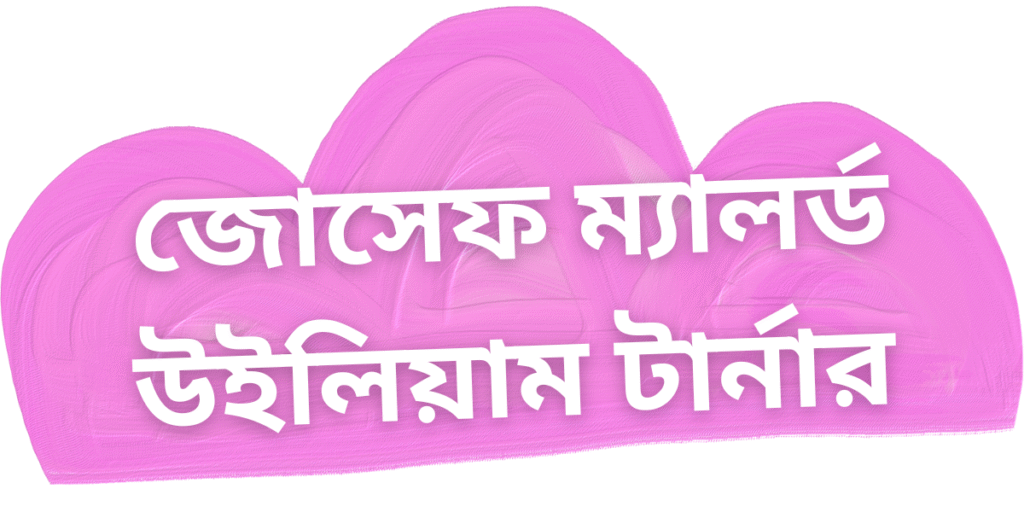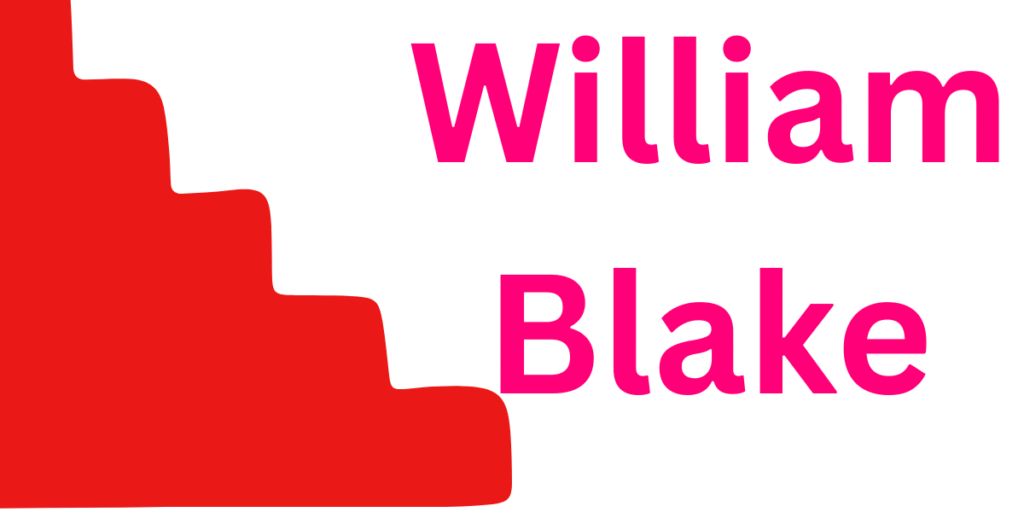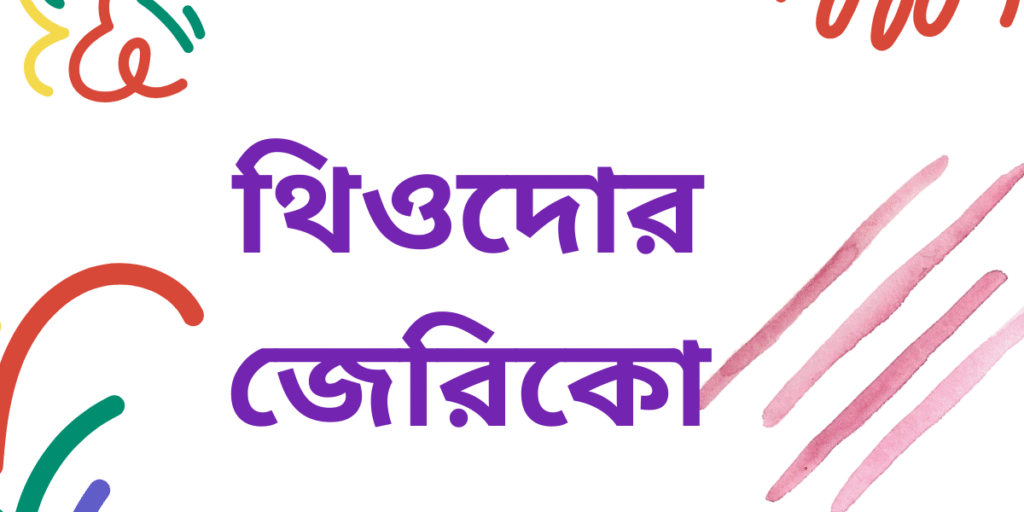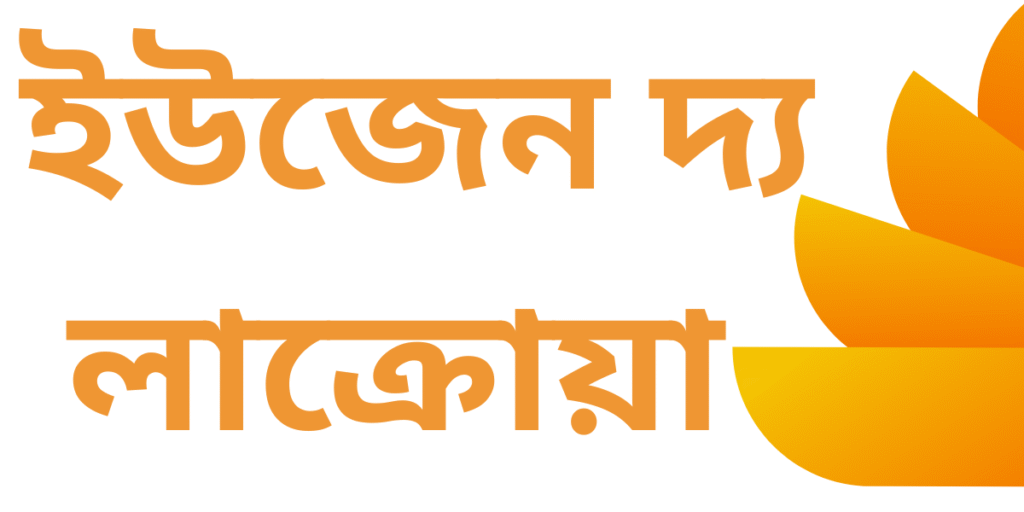জ্যাক-লুই ডাভিদ
জ্যাক-লুই ডাভিদের জন্ম ৩০ আগস্ট, ১৭৪৮ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে।
তাঁর পূর্ণ নাম ছিল Jacques-Louis David।
তিনি ছিলেন ইউরোপীয় নবশৈল্পিক (Neoclassical) শিল্প আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চিত্রশিল্পী।
তাঁর কাজ প্রাচীন গ্রিস ও রোমের শৈল্পিক গাম্ভীর্য দ্বারা অনুপ্রাণিত।
ডাভিদ ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের একজন দৃঢ় সমর্থক।
তাঁর শৈল্পিক জীবন রাজনীতি ও আদর্শের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল।
তিনি Rococo ধারা থেকে সরে এসে কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নৈতিক নবশৈল্পিক শৈলীতে কাজ করেন।
তাঁর বাবা যখন তিনি নয় বছর বয়সী, তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হন।
মা তাঁকে তাঁর চাচার কাছে পাঠান, যিনি ছিলেন স্থপতি।
ডাভিদ প্রথমে স্থাপত্যে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু পরে চিত্রকলায় মনোনিবেশ করেন।
তিনি François Boucher-এর ছাত্র ছিলেন, যিনি রোকোকো ধারার বিখ্যাত শিল্পী।
পরে তিনি Joseph-Marie Vien-এর অধীনে পড়াশোনা করেন, যিনি নবশৈল্পিকতার অগ্রদূত।
১৭৭৪ সালে তিনি Prix de Rome (রোম পুরস্কার) জেতেন।
এই পুরস্কারের মাধ্যমে তিনি রোমে অধ্যয়নের সুযোগ পান।
রোমে তিনি প্রাচীন রোমান ও গ্রিক শিল্প ও ভাস্কর্য অধ্যয়ন করেন।
তাঁর শিল্পচেতনায় শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও বীরত্ব ছিল মুখ্য বিষয়।
তাঁর প্রথম দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল “The Oath of the Horatii” (১৭৮৪)।
এই চিত্রটি নবশৈল্পিক আন্দোলনের ঘোষণাপত্রের মতো ধরা হয়।
এতে দেশপ্রেম, কর্তব্য ও আত্মত্যাগের প্রতীক ফুটে ওঠে।
তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে বিপ্লবী নৈতিকতা ও নাগরিক আদর্শ প্রকাশ করেন।
১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।
তিনি Jacobin দলে যোগ দেন এবং Maximilien Robespierre-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হন।
তিনি বিপ্লবী সরকারের জন্য চিত্র আঁকতেন ও জনসমাবেশ সংগঠনে ভূমিকা রাখতেন।
তিনি Robespierre-এর পতনের পর কিছু সময়ের জন্য কারাবন্দি ছিলেন।
ডাভিদ ছিলেন “পেন্টার অফ দ্য রেভোলিউশন” নামে পরিচিত।
তাঁর বিপ্লবী চিত্রগুলির মধ্যে “The Death of Marat” (১৭৯৩) সবচেয়ে বিখ্যাত।
এই চিত্রে বিপ্লবী নেতা Jean-Paul Marat-এর মৃত্যুকে বীরত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
এতে দেখা যায়—রাজনৈতিক শহীদের মর্যাদা পেয়েছে শিল্পে।
এই কাজটিকে নবশৈল্পিকতা ও রাজনৈতিক প্রচারণার মিশ্রণ বলা হয়।
তিনি নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে শিল্পে রূপান্তরিত করতে পটু ছিলেন।
বিপ্লব শেষে তিনি Napoleon Bonaparte-এর সমর্থক হয়ে ওঠেন।
নেপোলিয়নের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ডাভিদের জীবনও নতুন পথে এগোয়।
তিনি নেপোলিয়নের আনুষ্ঠানিক রাজচিত্রশিল্পী (court painter) হন।
তিনি নেপোলিয়নকে বীরত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক চরিত্রে উপস্থাপন করেন।
তাঁর বিখ্যাত চিত্র “Napoleon Crossing the Alps” (১৮০১) এই ধারার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
এই চিত্রে নেপোলিয়নকে বীরের মতো ঘোড়ার পিঠে দেখানো হয়েছে।
এটি ছিল প্রচারণামূলক শিল্প, কিন্তু একইসাথে মহাকাব্যিক রোমান্সও ধারণ করে।
তিনি নেপোলিয়নের রাজাভিষেকের বিশাল চিত্র আঁকেন—“The Coronation of Napoleon” (১৮০৭)।
এই চিত্রে নেপোলিয়নের মুকুট পরানোর মুহূর্তকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
এটি প্রায় ৬ মিটার উচ্চতা ও ১০ মিটার প্রস্থের বিশাল ক্যানভাস।
ডাভিদ তাঁর সময়ের সবচেয়ে ক্ষমতাবান শিল্পীদের একজন ছিলেন।
তিনি বহু ছাত্রকে শিক্ষা দেন, যারা পরে ইউরোপজুড়ে প্রভাব বিস্তার করে।
তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন Jean-Auguste-Dominique Ingres, যিনি নবশৈল্পিকতার উত্তরাধিকার বহন করেন।
ডাভিদের স্টুডিও ছিল নবশৈল্পিক আন্দোলনের কেন্দ্র।
তিনি কম্পোজিশন ও মানবদেহের গঠন নিয়ে কঠোর প্রশিক্ষণ দিতেন।
তাঁর প্রতিটি চিত্রে নাটকীয় গঠন, স্পষ্ট রেখা ও আলোর সুষম ব্যবহার দেখা যায়।
তিনি অলংকার ও আবেগের পরিবর্তে যুক্তি ও আদর্শকে গুরুত্ব দেন।
ডাভিদের কাজে আবেগ নিয়ন্ত্রিত, নীতিবোধ স্পষ্ট।
তাঁর শৈলী ছিল রোমান ভাস্কর্যের মতো নিখুঁত।
তিনি প্রায়ই চিত্রে তীক্ষ্ণ কনট্রাস্ট ও পাথরের মতো কঠিন ভঙ্গি ব্যবহার করতেন।
তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্প নৈতিকতা গড়ে তুলতে পারে।
তাঁর চিত্রে “কর্তব্য” ও “ত্যাগ” বারবার ফিরে আসে।
তিনি ইতিহাসচিত্রকে নৈতিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে দেখতেন।
তাঁর কাজ রাজনীতি, দর্শন ও সৌন্দর্যবোধের মিশ্রণ।
তিনি “Neo-classical morality” ধারার প্রতীক হয়ে ওঠেন।
তাঁর চিত্রকর্মের চরিত্রগুলোকে অনেক সময় বাস্তব মানুষ থেকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।
ডাভিদ ছিলেন অত্যন্ত নিখুঁত ও ধৈর্যশীল শিল্পী।
তিনি প্রতিটি রেখা, ছায়া ও দেহভঙ্গি নিয়ে গভীরভাবে কাজ করতেন।
তাঁর চিত্রকর্মে নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি ও স্থিরতা একসাথে দেখা যায়।
তিনি একবার বলেছিলেন—“Art must be political, but noble.”
নেপোলিয়নের পতনের পর ডাভিদ নির্বাসিত হন।
১৮১৬ সালে তিনি বেলজিয়ামের ব্রাসেলস-এ চলে যান।
সেখানেই জীবনের শেষ বছরগুলো কাটান।
নির্বাসনে থেকেও তিনি চিত্র আঁকা বন্ধ করেননি।
তাঁর শেষ দিকের একটি বিখ্যাত কাজ হলো “Mars Being Disarmed by Venus and the Graces” (১৮২৪)।
এই কাজটি তাঁর ক্লাসিক ধারার এক নরম, কাব্যিক রূপ প্রকাশ করে।
তিনি ফরাসি রাজতন্ত্রের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণে ফ্রান্সে ফিরে আসেননি।
ডাভিদের মৃত্যু হয় ২৯ ডিসেম্বর, ১৮২৫ সালে ব্রাসেলসে।
তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।
মৃত্যুর পর তাঁর দেহ বেলজিয়ামে সমাধিস্থ করা হয়।
ফ্রান্সে তাঁর মরদেহ ফিরিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল।
তবে তাঁর হৃদয় পরে ফ্রান্সে নিয়ে আসা হয় এবং Père Lachaise সমাধিক্ষেত্রে রাখা হয়।
তাঁর প্রভাব ইউরোপের প্রায় সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে।
১৯শ শতকের গোড়ায় নবশৈল্পিক ধারার প্রতিটি শিল্পী তাঁর প্রভাবে গঠিত হয়।
তিনি Ingres, Gros, এবং Gérard-এর মতো শিল্পীদের শিক্ষক ও প্রেরণা ছিলেন।
তাঁর শিল্পকর্ম রাজনৈতিক, নৈতিক ও সৌন্দর্যচেতনার নিখুঁত সমন্বয়।
ডাভিদের চিত্রাবলী বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ জাদুঘরে সংরক্ষিত।
তাঁর অনেক কাজ Louvre Museum (Paris)-এ রয়েছে।
তাঁর চিত্রগুলি ইতিহাসের শিক্ষামূলক নথির মতো।
তাঁর শিল্প রোমান প্রজাতন্ত্রের বীরত্ব ও নাগরিক দায়িত্ববোধের প্রশংসা করে।
“The Death of Socrates” (১৭৮৭) তাঁর আরেকটি বিখ্যাত চিত্র।
এই চিত্রে দার্শনিক সক্রেটিসের আত্মত্যাগের দৃশ্য অমর করে তুলেছেন।
এটি যুক্তিবাদ, নীতি ও কর্তব্যের আদর্শকে উদযাপন করে।
ডাভিদের এই চিত্র প্রাচীন নীতিবাদকে আধুনিক যুগে ফিরিয়ে আনে।
তাঁর প্রতিটি কাজেই দর্শনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে উপস্থিত।
তিনি নান্দনিকতার চেয়ে আদর্শবাদকে প্রাধান্য দিতেন।
নবশৈল্পিকতার মাধ্যমে তিনি রোকোকো ধারার বিলাসিতা ও আবেগবোধকে প্রত্যাখ্যান করেন।
তাঁর কাজ “পাবলিক আর্ট” ও “নৈতিক শিক্ষার মাধ্যম” হিসেবে কাজ করত।
ফরাসি বিপ্লবের সময় তাঁর চিত্রগুলো জনগণকে উদ্দীপ্ত করত।
তিনি ছিলেন শিল্পী, শিক্ষক, বিপ্লবী ও প্রচারক—সব একসাথে।
ডাভিদের আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা তাঁর প্রতিটি ক্যানভাসে দেখা যায়।
তিনি নারীচিত্র খুব কম এঁকেছেন, এবং তাও নৈতিক বা পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে।
তাঁর প্রতিটি পুরুষচিত্রে বীরত্ব, দৃঢ়তা ও আদর্শবাদ ফুটে ওঠে।
তাঁর শিল্প ইতিহাসকে শুধু পুনর্নির্মাণ নয়, পুনর্গঠন করেছে।
তাঁর ছাত্ররা পরবর্তীকালে রোমান্টিক আন্দোলনের সূচনা করে।
ডাভিদ ছিলেন নবশৈল্পিকতার সর্বোচ্চ স্রষ্টা ও সমাপ্তিও।
তাঁর জীবন দেখায়—শিল্প কেবল সৌন্দর্য নয়, আদর্শের অস্ত্রও হতে পারে।
তাঁকে বলা হয় “The Moral Painter of the Revolution।”
আজও তাঁর চিত্রগুলো রাজনৈতিক ও নৈতিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে অধ্যয়ন করা হয়।
জ্যাক-লুই ডাভিদ ফরাসি ইতিহাসে “চিত্রকলার বিপ্লবী” হিসেবে অমর।