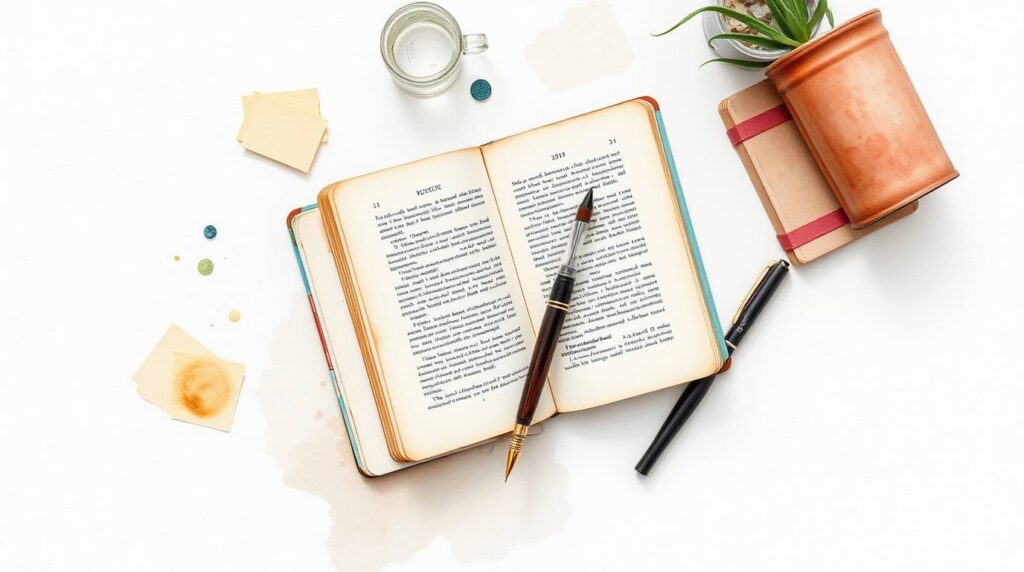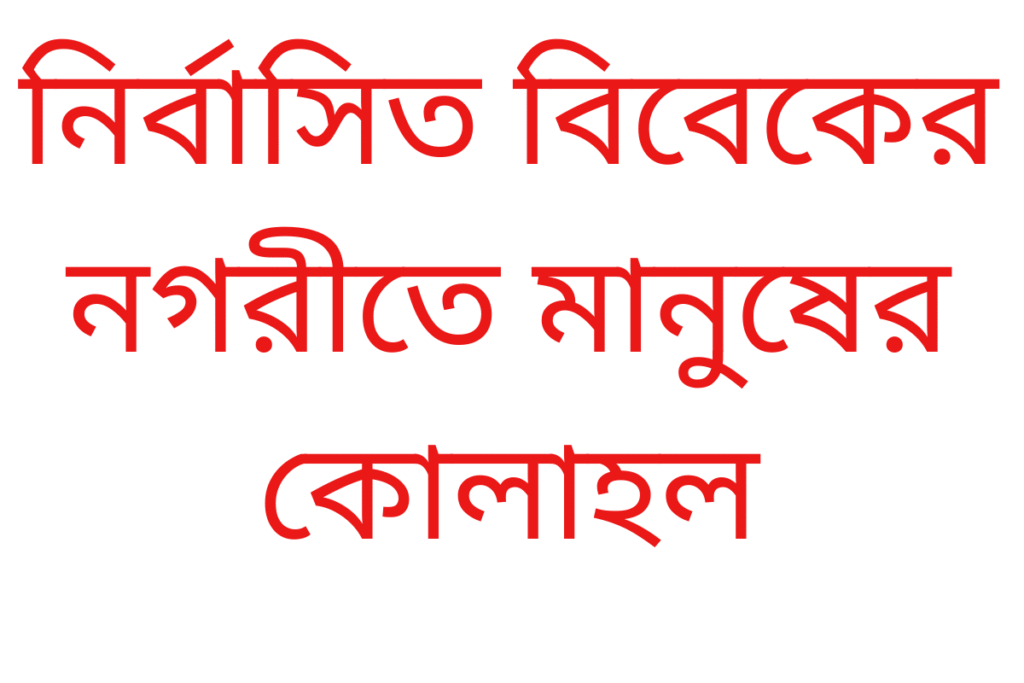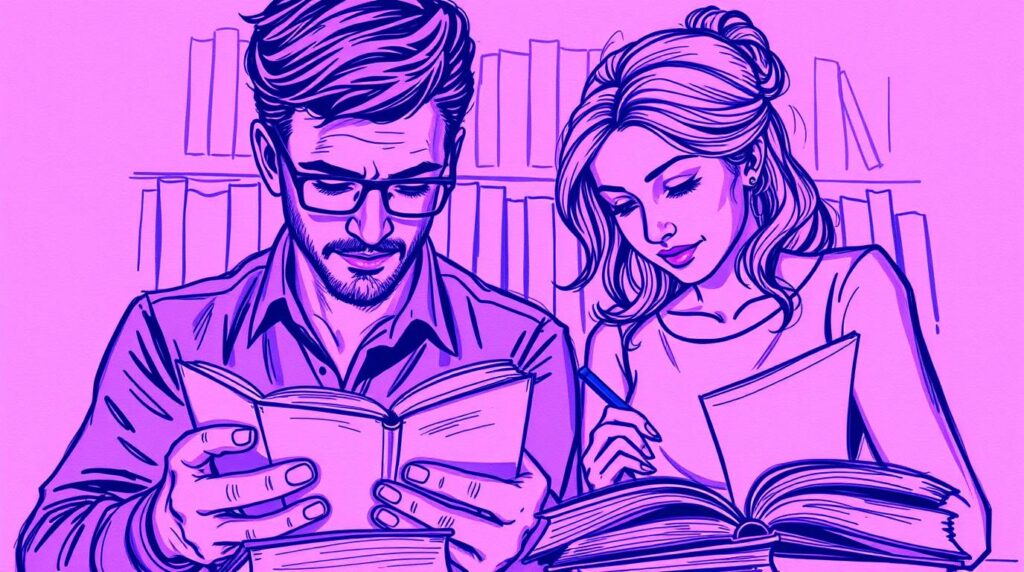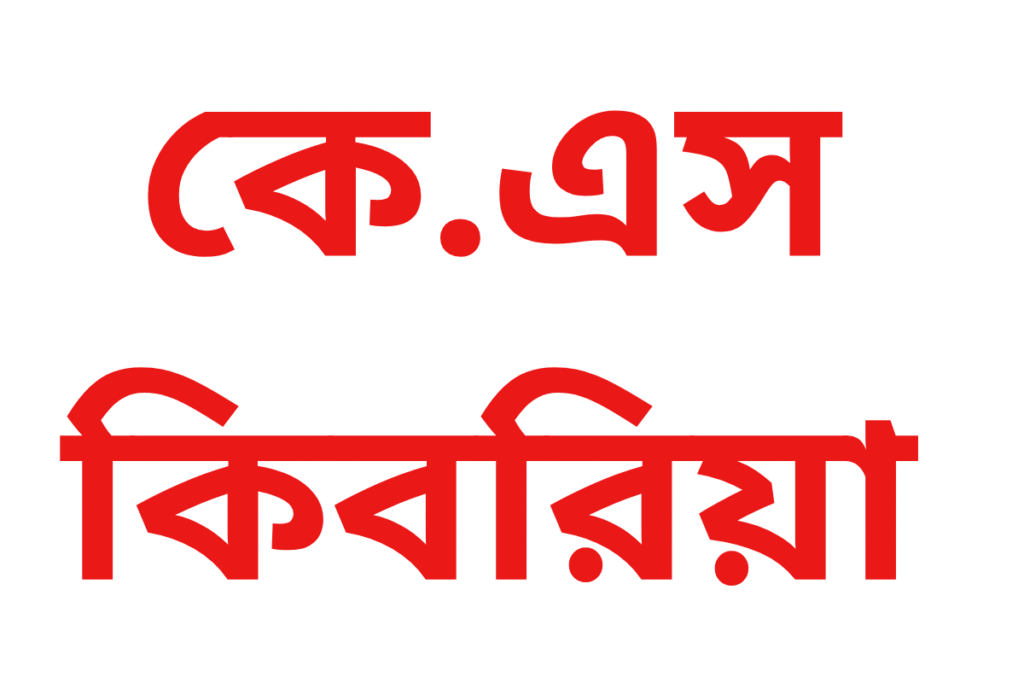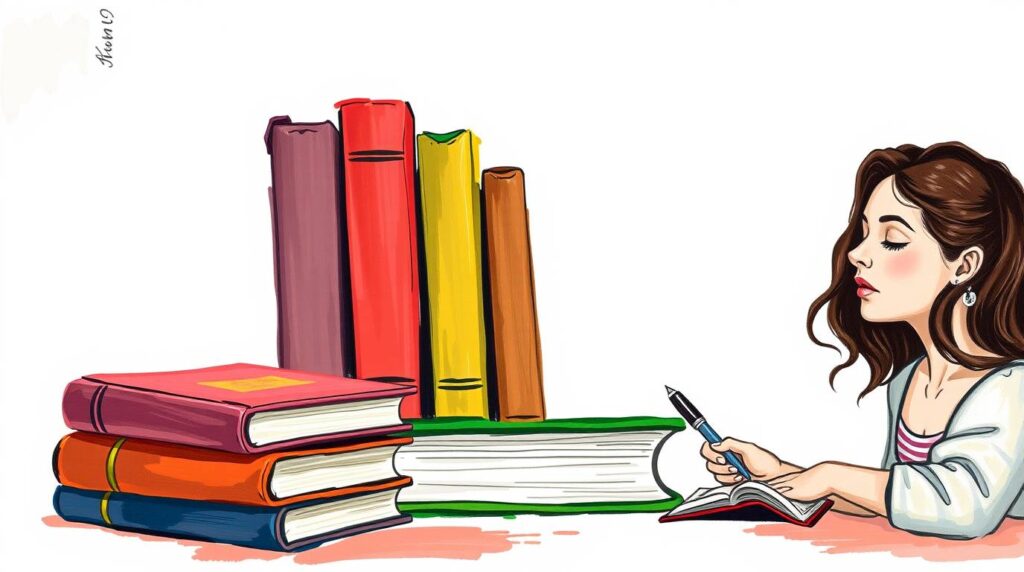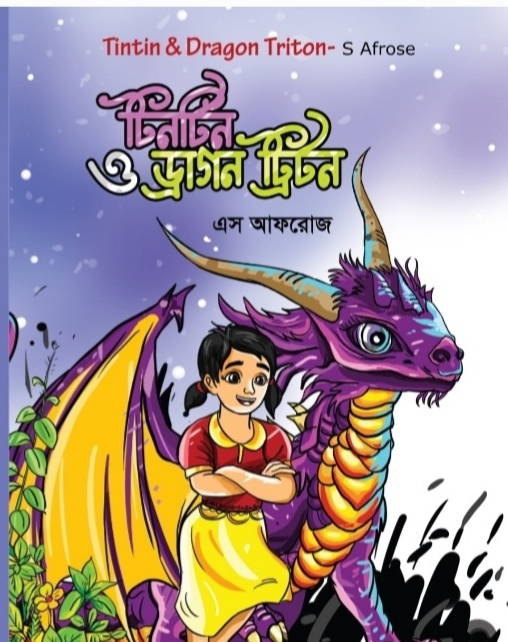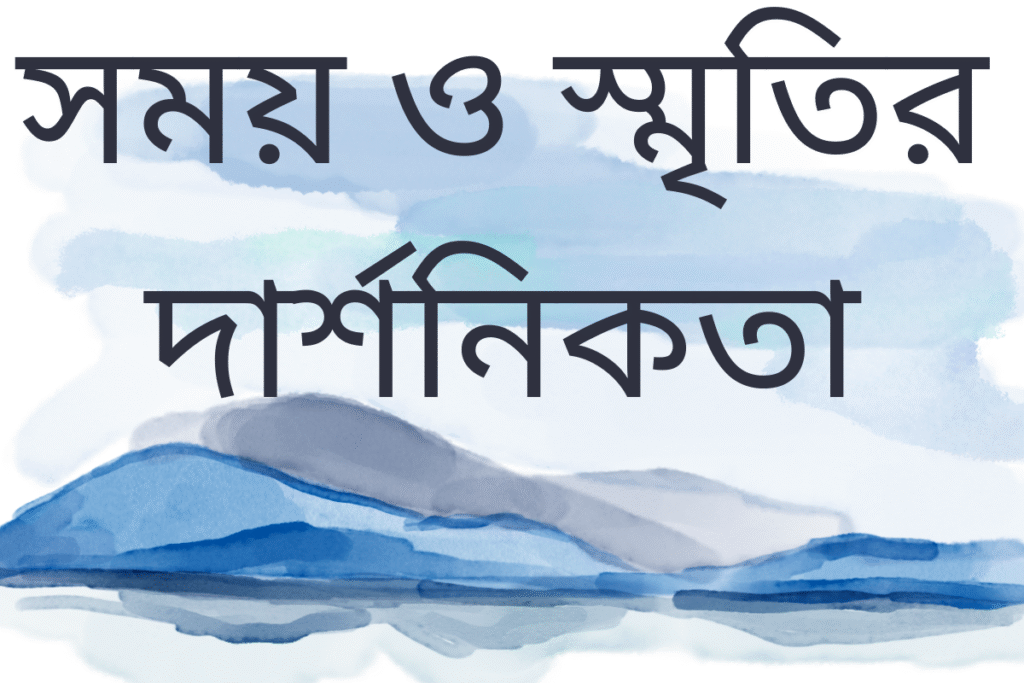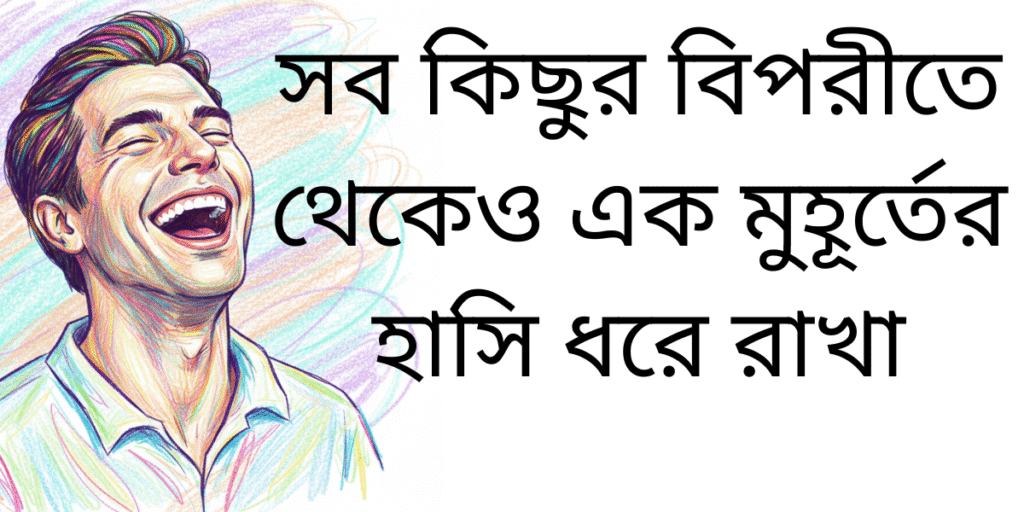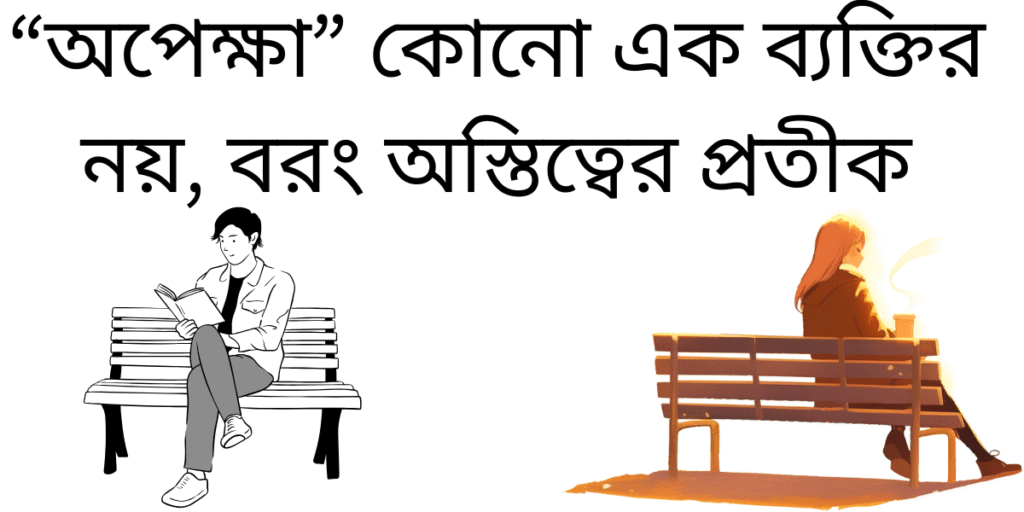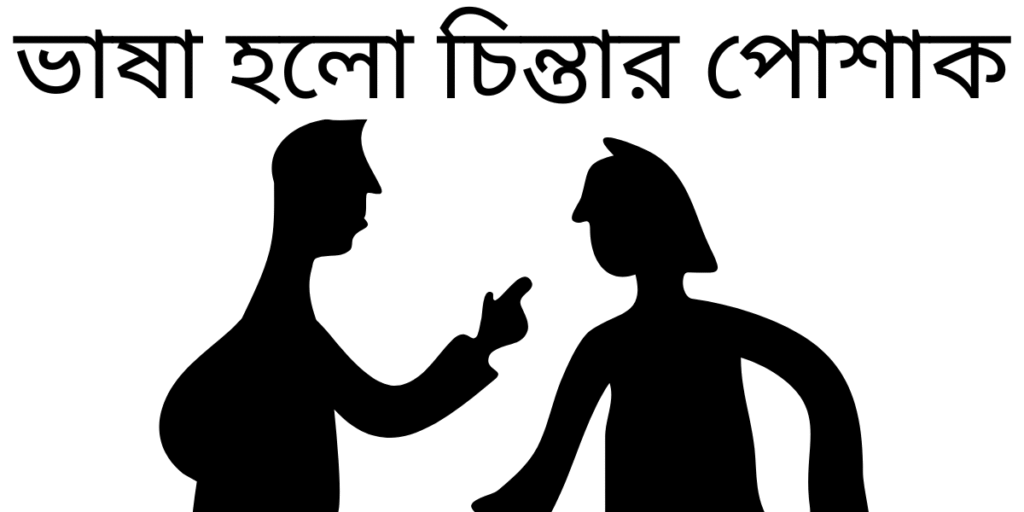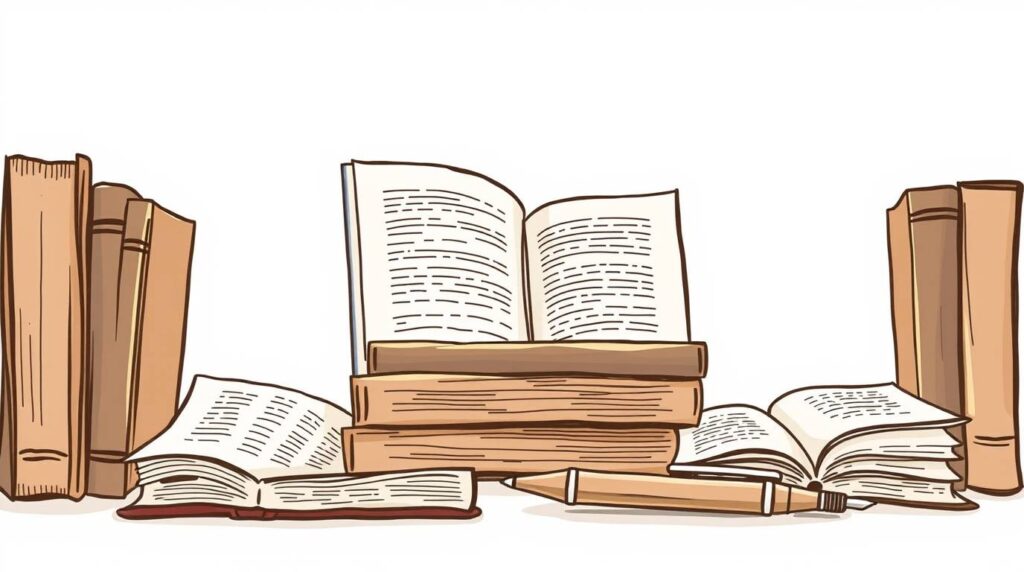১৭শ শতকের নিউ ইংল্যান্ড ছিল অস্থিরতার রণক্ষেত্র—ইউরোপীয় বসতি, নেটিভ আমেরিকান উপজাতি, ধর্মীয় মতাদর্শ, রাজনীতি ও ভূমির দখলদারির দ্বন্দ্বে অঞ্চলজুড়ে তৈরি হচ্ছিল টানটান উত্তেজনা। এই উত্তপ্ত সময়েই ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন মেরি রাওল্যান্ডসন—যাঁর বন্দিদশার অভিজ্ঞতা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত দুর্ভোগের গল্প নয়, বরং উপনিবেশিক মনের ভিতরকার দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক, এবং পুরিতান সমাজের আত্মরক্ষামূলক মনোভাবের এক প্রামাণ্য দলিল।
“The Sovereignty and Goodness of God”—এই গ্রন্থটি শুধু আমেরিকান সাহিত্যে Indian Captivity Narrative নামক ধারার সূচনা করে না, বরং উপনিবেশিক ইতিহাস ও ধর্মীয় সাহিত্য উভয় ধারাতেই একটি অনন্য স্থান অধিকার করে। রাওল্যান্ডসনের চোখ দিয়ে আমরা দেখি—যুদ্ধের বিভীষিকা, মানবীয় সহনশীলতা, খাদ্য-সংকট, মায়ের ভাঙন ও শক্তি, এবং সর্বোপরি তাঁর বিশ্বাসের শিকড়ে শিকড়ে লেগে থাকা ঈশ্বর-নির্ভরতা।
এক. প্রাথমিক জীবন ও পুরিতান সমাজের প্রেক্ষাপট
১৬৩৭ সালে ইংল্যান্ডের সোমারসেটে জন্ম নেওয়া মেরি রাওল্যান্ডসন শৈশবেই পরিবারসহ নিউ ইংল্যান্ডে অভিবাসন করেন। তখনকার পুরিতান সমাজ ছিল কঠোর ধর্মীয় শৃঙ্খলার ওপর দাঁড়ানো—মানুষের প্রতিটি কাজ, অনুভূতি ও সংকট ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে বিবেচিত হত। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরে রাওল্যান্ডসনের বয়ানে গভীর ছাপ ফেলেছিল।
তাঁর স্বামী রেভারেন্ড জোসেফ রাওল্যান্ডসন ছিলেন ল্যাঙ্কাস্টার (Massachusetts) শহরের ধর্মযাজক। সমাজে সম্মানিত হলেও পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল না, আর উপনিবেশিক গ্রামগুলো তখন নেটিভ আমেরিকানদের আক্রমণে বিপদসংকুল। ১৬৭০-এর দশকে উপনিবেশ সম্প্রসারণের ফলে আদিবাসী উপজাতিগুলির সঙ্গে সংঘাত তীব্র হয়ে উঠে—বিশেষত ওয়াম্পানোয়াগ, নারাগানসেট, এবং নিপমুক উপজাতিরা ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকে তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে দেখছিল।
এই সব উত্তেজনার কেন্দ্রেই ঘটে King Philip’s War (১৬৭৫–১৬৭৬)—যার ভেতরেই শুরু হয় রাওল্যান্ডসনের জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ অধ্যায়।
দুই. বন্দিত্বের সূচনা: ল্যাঙ্কাস্টার আক্রমণ
১৬৭৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ভোর। ঘন বরফে ঢাকা ল্যাঙ্কাস্টার শহর হঠাৎ করে আক্রমণ করে বসে নেটিভ আমেরিকানদের একটি বিশাল দল। রাওল্যান্ডসন তাঁর বর্ণনায় জানান, বাড়ির চারপাশে লেলিহান আগুন, বধির করা চিৎকার, গুলির ঝড়—সব মিলিয়ে মৃত্যু যেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল দরজার কাছে। তাঁর পরিবার পালাতে না পেরে ঘরের ভিতরেই আটকা পড়ে যায়।
এই আক্রমণে তাঁর বহু স্বজন নিহত হন। রাওল্যান্ডসন নিজে আহত হন; তাঁর ছয় বছরের কন্যা সারাহও গুরুতর আহত হয়। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই তাঁদের বন্দি করে নিয়ে যায় নেটিভ বাহিনী—যা পরিণত হয় প্রায় ১১ সপ্তাহ দীর্ঘ এক বিভীষিকাময় যাত্রায়।
তিন. বন্দিদশার অভিজ্ঞতা: বাস্তবতা, দুঃখ ও টিকে থাকার সংগ্রাম
রাওল্যান্ডসন তাঁর বর্ণনায় বন্দিত্বের প্রতিটি ধাপকে বলেছেন “remove”—অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন, যা প্রতিবারই তাঁর জীবনে নতুন বিপর্যয় ও নতুন সহনশীলতার পরীক্ষা নিয়ে আসে। এসব “remove”–এ আমরা পাই—
১. শারীরিক নিপীড়নের গল্প নয়
অনেকে মনে করেন তিনি নেটিভদের দ্বারা কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন—কিন্তু তাঁর বর্ণনায় শারীরিক নিপীড়নের উল্লেখ খুব কম। বরং তিনি বলেছেন তাঁকে সাধারণত কাজে লাগানো হতো—খাদ্য প্রস্তুত, পোশাক তৈরির কাজ ইত্যাদি।
২. খাদ্যের জন্য সংগ্রাম
ক্ষুধার কষ্ট ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন। কখনও “horse liver”, কখনও ধোঁয়ায় শুকানো সামান্য কর্ন—যা আমেরিকান আদিবাসীদের স্বাভাবিক খাদ্য হলেও তাঁর কাছে ছিল অস্বাভাবিক ও প্রায় অখাদ্য।
৩. ধর্মবিশ্বাস ছিল একমাত্র আশ্রয়
তিনি প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে বাইবেলের পদ উল্লেখ করেছেন, যেন ঈশ্বর তাঁর কষ্টকে কোনো পরীক্ষা হিসেবে পাঠিয়েছেন। এই ধর্মীয় কাঠামো তাঁর মানসিক স্থিতি রক্ষা করে।
৪. নেটিভ আমেরিকানদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি
তখনকার পুরিতান সমাজে নেটিভদের সাধারণত “অসভ্য” বা “পাপী” হিসেবে দেখা হতো। রাওল্যান্ডসনও প্রথমদিকে তাঁদের সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। তবে বর্ণনার গভীরে দেখা যায়—তিনি তাঁদের সাহস, পারস্পরিক সহায়তা, এবং পরিবারবন্ধনের স্বীকৃতি দিয়েছেন। চরম বিপর্যয়ের মাঝে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে জটিলতর হয়েছে।
৫. মাতৃত্বের বেদনা
বন্দিত্বের সময় তাঁর কন্যা সারাহ মারা যায়। এই মৃত্যু তাঁর বইয়ের সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী অংশ—যেখানে তিনি মায়ের অসহায়ত্ব ও বেদনার কথা লিখেছেন ব্যথিত ভাষায়।
৬. নেটিভদের অভ্যন্তরীন জীবন
রাওল্যান্ডসন নেটিভ মহিলাদের রান্না, শিশুসেবা, শিকার-উৎসব, দুঃখ-সঙ্গীত—সবই পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ কারণেই তার বই নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও মূল্যবান দলিল।
১১ সপ্তাহ পর তাঁর মুক্তির জন্য উপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ২০ পাউন্ড মুক্তিপণ প্রদান করে। রাওল্যান্ডসন ফিরে আসেন কাঠখোট্টা কিন্তু পরিশীলিত আত্মবিশ্বাস নিয়ে—যেন বেদনাই তাঁকে নতুন করে তৈরি করেছে।
চার. গ্রন্থ প্রকাশ: “The Sovereignty and Goodness of God”
১৬৮২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত বর্ণনা। এটি আমেরিকান সাহিত্যের প্রথম দিকের বেস্টসেলার—ইংল্যান্ডেও প্রকাশিত হয়েছিল একাধিকবার।
বইয়ের মূল বৈশিষ্ট্য
ধর্মীয় ব্যাখ্যা: ঘটনা-অভিজ্ঞতাকে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে বুঝেছেন।
বন্দিত্বের বিশদ বর্ণনা: প্রতিটি remove–এর বিবরণ মানসিক নথির মতো মনে হয়।
আত্মরক্ষার কৌশল: সামঞ্জস্য, adapt করা, শান্ত থাকা—এসব মনস্তাত্ত্বিক দিক বইটিকে বিশেষ করে তোলে।
নেটিভদের চিত্রণ: পক্ষপাত থাকলেও মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে।
পাঁচ. রাওল্যান্ডসনের বয়ান: ধর্ম, ভয় ও পরিচয়ের রাজনীতি
১. পুরিতান ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব
তিনি মনে করতেন প্রতিটি বিপর্যয় ঈশ্বরের পরীক্ষামূলক পরিকল্পনার অংশ। বন্দিত্বের বর্ণনায় তাঁর ধর্মীয় ভাষা একটি প্রতিরোধক শক্তি তৈরি করেছিল।
২. নারী–অভিজ্ঞতার অনাবিষ্কৃত কণ্ঠস্বর
রাওল্যান্ডসনের বর্ণনা উপনিবেশিক নারীর ভয়, সংকট, বেঁচে থাকা ও জ্ঞানের এক সাহসী দলিল। তাঁর লেখায় আমরা পাই—
নারী হিসেবে সামাজিক সীমাবদ্ধতা,
মাতৃত্বের যন্ত্রণায় মানসিক শক্তি,
অমানবিক পরিস্থিতিতে স্বনির্ভরতার পাঠ।
৩. নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ
অবচেতনে হলেও তিনি নেটিভ সমাজের খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক সম্পর্ক, পোশাক, যুদ্ধনীতি ইত্যাদির মূল্যবান উপাত্ত তুলে ধরেছেন।
৪. উপনিবেশিক রাজনীতি
এই বই নেটিভ–উপনিবেশিক সম্পর্ক সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। তবে আজকের গবেষকেরা দেখেন—রাওল্যান্ডসন দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন; তাঁর ভয় ও মানবিক উপলব্ধি একইসঙ্গে কাজ করেছিল।
ছয়. Indian Captivity Narrative ধারার সূচনা
রাওল্যান্ডসনের বই পরে আমেরিকায় একটি বড় সাহিত্যিক ধারার জন্ম দেয়—Indian Captivity Narrative। এই ধারায় দেখা যায়—
বন্দিত্ব,
ভয়ের মোকাবিলা,
ধর্ম বা সভ্যতার আশ্রয়,
শেষপর্যন্ত মুক্তির পর সমাজে পুনরাগমন।
অনেক পরবর্তী লেখক—পুরুষ ও নারী উভয়ই—তাঁর পথ ধরে একই ধরনের বর্ণনা লিখেছেন। তাঁর বই তাই আমেরিকান আখ্যানের এক শক্ত ভিত।
সাত. নেটিভ আমেরিকানদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিক মূল্যায়ন
আধুনিক গবেষণা রাওল্যান্ডসনকে একরৈখিক চোখে দেখে না।
১. তাঁর ভয়–ভিত্তিক পক্ষপাত
বন্দিত্বের চাপ, পুরিতান মূল্যবোধ ও উপনিবেশিক সংস্কৃতি তাঁকে নেটিভদের “অসভ্য” হিসেবে দেখতে শিখিয়েছিল।
২. মানবিক উপলব্ধি
বইয়ের বিভিন্ন স্থানে তিনি স্বীকার করেছেন—
তাঁকে কেউ খাবার দিয়েছে,
শিশুকে সান্ত্বনা দিয়েছে,
অন্যায় আচরণেরও প্রতিবাদ হয়েছে।
অর্থাৎ নেটিভদের তিনি সম্পূর্ণভাবে একরকমভাবে দেখেননি। তাঁর বর্ণনা তাই মানবিক ও জটিল।
আট. আমেরিকান সাহিত্য ইতিহাসে তাঁর স্থায়ী গুরুত্ব
১. প্রথম আমেরিকান মহিলা লেখক হিসেবে পরিচিতি
যদিও তাঁর আগেও নারী লেখক ছিলেন, কিন্তু রাওল্যান্ডসন প্রথম যিনি নিজের জীবনকে সাহিত্যীয় কাঠামোয় রূপ দিয়েছেন এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।
২. আত্মজৈবনিক সাহিত্যের প্রাথমিক রূপ
তাঁর বই আমেরিকান আত্মজৈবনিক ধারার পূর্বসূরি।
৩. ন্যারেটিভ আর্টের অভিনবতা
তিনি উত্তেজনা তৈরি, ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও বেদনাকে কাব্যিক ঢংয়ে উপস্থাপন করেছেন।
৪. সমাজ–ইতিহাসের দলিল
১৭শ শতকের উপনিবেশ, যুদ্ধ, নারী–অবস্থান, ধর্মীয় সংস্কৃতি—সবই তাঁর লেখায় সংরক্ষিত।
নয়. রাওল্যান্ডসনের পরবর্তী জীবন
মুক্তির পরে তিনি স্বামীর সঙ্গে ফিরে আসেন। কিছু বছর পর তাঁর স্বামী মারা গেলে তিনি আবার বিবাহ করেন—কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি কখনো লেখালেখিতে উল্লেখযোগ্যভাবে ফিরে আসেননি।
১৭১১ সালে তিনি মারা যান। কিন্তু তাঁর বই বেঁচে থাকে—ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে, সাহিত্যিক পাঠ হিসেবে, এবং মানব আত্মার সহনশীলতার এক কালজয়ী প্রতীক হিসেবে।
মেরি রাওল্যান্ডসনের বর্ণনা শুধুই বন্দিত্বের ডায়েরি নয়; এটি এক যুগের মন, ভয়, ধর্ম, রাজনীতি, এবং আত্মসংঘাতের ইতিহাস। অগ্নিকুণ্ড দিয়ে হাঁটার মতো সেই ১১ সপ্তাহ তাঁকে যেমন বদলে দিয়েছে, তেমনই বদলেছে আমেরিকান সাহিত্যেও নারী–স্বরে বলার প্রচলন।
তার বইয়ের বাক্যগুলো আজও পাঠকমনে দুলে ওঠে—এক নারীর অটল বিশ্বাস, ক্ষুধায়-তাড়িত দিনের স্মৃতি, সন্তানহারা মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ, আর অচেনা মানুষের ভিতরে মানবতার ক্ষুদ্র আলো খুঁজে পাওয়ার মতো গভীর অভিজ্ঞতা নিয়ে।
রাওল্যান্ডসন যেন আমাদের জানান—
মানুষ কখনও পুরোপুরি একরঙা নয়; সংকট মানুষকে জটিলতর করে তোলে, আর সেই জটিলতার ভেতরেই লুকানো থাকে ইতিহাসের সত্য।