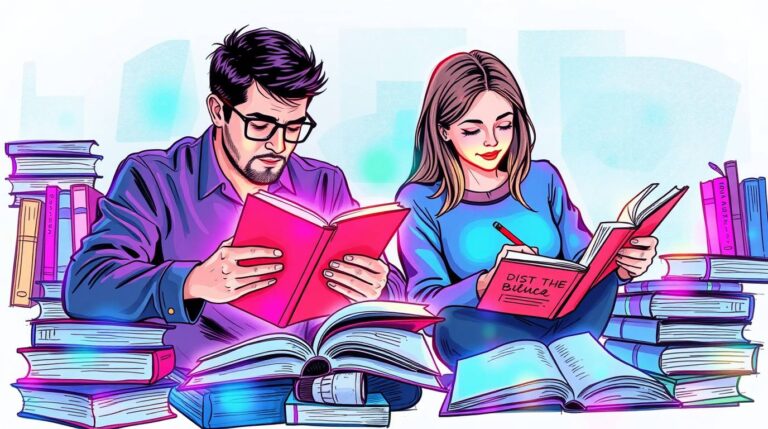The Art of Fiction: Notes on Craft for Young Writers by John Gardner
“সৌন্দর্যগত বিধি ও শৈল্পিক রহস্য”
জন গার্ডনার ভূমিকায় প্রথমেই স্পষ্ট করেন যে কথাসাহিত্য রচনার মূলে থাকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি: (১) পাঠকের মনে একটি “জীবন্ত ও ধারাবাহিক স্বপ্ন”-এর জগৎ তৈরি করা, এবং (২) “সৌন্দর্যগত আইন” অনুসরণ করা। এই সৌন্দর্যগত আইন কোনো নির্দিষ্ট নিয়মকানুনের কাঠামো নয়; বরং এমন কিছু মূলনীতি যা গল্পকে ঐক্যবদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য অপরিহার্য।
গার্ডনারের দৃষ্টিতে, সফল কথাসাহিত্যে সবসময় একপ্রকার রহস্য বা ম্যাজিক থাকে যা শুধুমাত্র কারিগরি দক্ষতা দিয়ে তৈরি করা যায় না। লেখকের ব্যক্তিগত কল্পনাশক্তি, মানসিক স্বচ্ছতা ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি একসঙ্গে মিলে যায় বলেই এই ম্যাজিক তৈরি হয়। অনুপ্রেরণা এবং টেকনিক—উভয়ই দরকার। লেখককে যেমন ভাষা ও রচনার শৈল্পিক দিকগুলোতে নিখুঁত হতে হবে, তেমনি গভীর আবেগ এবং নৈতিক অন্তর্দৃষ্টিও অর্জন করতে হবে, যাতে গল্প পাঠকের মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলতে পারে।
ভূমিকায় গার্ডনার বলেন, গল্প যত উন্নত বা সাধারণ হোক, সেটি গড়ে ওঠে নিবিড় পুনর্লিখন, ভাষায় যত্ন ও থিমের অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে। সঙ্গে থাকছে সেই অদৃশ্য “অনুপ্রেরণার ঝলক,” যা লেখককে পরিচিত সীমানার বাইরে নিয়ে যায়। সুতরাং, প্রতিটি অধ্যায়ে গার্ডনার এই দ্বৈত রূপরেখাকেই এগিয়ে নিয়ে যাবেন: শৈল্পিক স্পর্শের সঙ্গে কারিগরি নিয়ন্ত্রণের মিশেল।
অধ্যায় ১: “মৌলিক দক্ষতা, ধারা, এবং স্বপ্নের মতো কথাসাহিত্য”
প্রথম অধ্যায়ে গার্ডনার তাঁর বিখ্যাত “ফিকশনাল ড্রিম” বা “কল্পিত স্বপ্ন”-এর ধারণা উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, কথাসাহিত্যের কাজই হলো এমন একটি বাস্তব অনুভূতি দেওয়া যাতে পাঠকরা বই হাতে নিয়ে সেই দুনিয়ায় সম্পূর্ণ ডুবে যেতে পারেন, যেন ঘটনাগুলো সত্যি ঘটছে। এই স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে দরকার স্পষ্ট ও সংবেদী বর্ণনা: চরিত্রদের ভাব-ভঙ্গি বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে, পরিবেশ-কাঠামো স্পষ্ট হতে হবে, এবং ঘটনাগুলো যেন যুক্তিসংগতভাবে ঘটতে পারে।
গার্ডনার মৌলিক ভাষাগত দক্ষতার ওপর জোর দেন—ব্যাকরণ, বাক্যগঠন ও শব্দচয়ন যেন নিখুঁত হয়। অতিরিক্ত নির্ধারিত নিয়মকানুনের কঠোরতা তিনি উড়িয়ে দেন, তবে অযত্নে লেখা কিংবা ব্যাকরণগত ভুলে পাঠক যেন গল্প থেকে বিচ্যুত না হন, সে বিষয়ে সতর্ক করেন।
এ ছাড়া গার্ডনার ধারাবিন্যাস (genre) বা সাহিত্যের প্রকরণ সম্পর্কে বলেন। তিনি লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেন, “আপনি যা লিখবেন—সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি কিংবা রিয়ালিস্টিক উপন্যাস—তা নিয়ে বেশি অস্বস্তি করবেন না, তবে প্রতিটি ধারা যে পাঠকের একধরনের প্রত্যাশা তৈরি করে, সেটাও আপনাকে বুঝতে হবে।” গল্পে সেই প্রত্যাশা হয় পূরণ করবেন, নয়তো সচেতনভাবে ভাঙবেন, কিন্তু যাই করুন, পাঠকের “স্বপ্ন” সচল রাখতে হবে।
অধ্যায় ২: “আকর্ষণ ও সত্য”
এই অধ্যায়ে গার্ডনার কথাসাহিত্যের দুটি প্রধান দায়িত্বের কথা বলেন: পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিল্পগত সত্য রক্ষা করা। “আগ্রহ” মানে শুধুমাত্র উত্তেজনা বা বিনোদন নয়; বরং পাঠককে চরিত্র, ঘটমান ঘটনা ও সংকটের মাঝে আবদ্ধ রাখতে হবে। লেখককে এমন পরিস্থিতি ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে হবে যেখানে পাঠক উত্তর খোঁজার, চরিত্রের ভাগ্য জানার বা অব্যক্ত জটিলতা উন্মোচনের প্রবল কৌতূহল বোধ করেন।
“সত্য” অর্থে গার্ডনার বোঝান বাস্তবসম্মত কারণ-ফলাফল এবং গভীরতর মানবিক বা নৈতিক সত্য। ঘটনাগুলো গল্পের অভ্যন্তরীণ যুক্তির সঙ্গে মেলে চলবে, চরিত্ররা বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। এমনকি ফ্যান্টাসি বা সায়েন্স ফিকশনেও মানুষ যে আবেগ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও মূল্যবোধের ভেতর বাস করে, সে সত্যটুকু রাখতে হবে।
গার্ডনার বলেন, লেখককে দ্ব্যর্থহীন বা সরলীকৃত অবস্থানের পরিবর্তে জটিলতায় মনোযোগ দিতে হবে। নৈতিক দ্বিধা বা আবেগের সূক্ষ্মতার মধ্য দিয়েই গল্পটি আরো অর্থবহ হয়ে ওঠে। যদি গল্পে কেবল পাঠককে আগ্রহী রাখার বাহানায় নানা ঘটনার পাশাপাশি গভীর কোনো মানবিক সত্য ফুটে না ওঠে, তবে সে গল্প হয়ে পড়বে ফাঁপা।
অধ্যায় ৩: “গল্পের সামগ্রিক গঠন”
এই অধ্যায়ে গার্ডনার বলেন, ভাল গল্প বা উপন্যাস কেবল বাক্য বা অনুচ্ছেদের সৌন্দর্যে সীমাবদ্ধ নয়; সামগ্রিকভাবে গল্পের অবয়ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অবয়বই গল্পের কাঠামোকে দৃঢ় করে: কোথায় শুরু হবে, কীভাবে দ্বন্দ্ব বাড়বে, কখন চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছাবে, এবং কীভাবে পরিণতি বা সমাধান ঘটবে—এসবই গল্পকে পূর্ণতা দেয়।
তিনি লেখকদের পরামর্শ দেন যে গদ্যের সূক্ষ্মতা নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত না থেকে, পুরো আখ্যানের ছক মাথায় রেখে কাজ করা জরুরি। একটি ভালো গল্পে শুরুর মুহূর্তটি পাঠককে টেনে আনে, মধ্যভাগে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব বাড়ে, আর শেষভাগে এসে তার যৌক্তিক কিন্তু পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক পরিসমাপ্তি ঘটে।
তবে গার্ডনার স্বীকার করেন, সব গল্প একইরকম ধাপে ধাপে চলে না। ফ্ল্যাশব্যাক বা নন-লিনিয়ার বর্ণনাকেও তিনি স্বাগত জানান, যদি সেগুলো গল্পের ঐক্য ও ছন্দকে রক্ষা করতে পারে। পেসিং বা গতিবেগ, অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক সংলাপ বা বর্ণনার দ্বারা যেন গল্পের ঝুঁকে যাওয়া না ঘটে। সামগ্রিক গঠন ঠিক রেখে লেখককে প্রতিটি অধ্যায় ও দৃশ্যকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে প্রতিটির আলাদা মূল্য ও অবদান থাকে।
অধ্যায় ৪: “মেটাফিকশন”
গার্ডনার এই অধ্যায়ে মেটাফিকশন নিয়ে আলোচনা করেন, অর্থাৎ এমন গল্প যা নিজেই নিজের আর্টিফ্যাক্ট বা নির্মিতি হিসেবে পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়। গল্পের মধ্যে গল্প বা স্ব-উৎখাত পরস্পর-সংলাপের মাধ্যমে মেটাফিকশন কখনও পাঠককে গল্পের গভীরে নিয়ে যেতে পারে, আবার কখনও হালকা বুদ্ধিদীপ্ত খেলা হিসেবে থাকতে পারে।
তবে গার্ডনার সাবধান করে বলেন, অনেক তরুণ লেখক মেটাফিকশন ব্যবহার করেন শুধুমাত্র “চালাক” বা “চাতুর্যময়” লেখকসত্তা প্রকাশের জন্য, অথচ বাস্তবিক মনস্তাত্ত্বিক বা নৈতিক গভীরতা সেই রচনায় অনুপস্থিত থাকে। এটি গল্পের স্বপ্নকে নষ্ট করে দিতে পারে।
যদি মেটাফিকশন সত্যিই চরিত্র, দ্বন্দ্ব কিংবা মূল থিমকে উন্নত করে বা গল্পের সাথে মৌলিকভাবে যুক্ত হয়, তবে তা সার্থক হতে পারে। অন্যথায় এটি মাত্রই কৌশল বা চমক হয়ে থেকে যায়, যার ফলে পাঠক শৈল্পিকভাবে তৃপ্তি পান না। সুতরাং, গার্ডনারের মতে, আত্মসচেতন বা স্ব-সন্দর্ভধর্মী টেক্সটকেও হৃদয়গ্রাহী হতে হলে পারদর্শী রচনার পাশাপাশি আসল আবেগ ও মানবিক সংশ্লেষ রাখতে হয়।
অধ্যায় ৫: “জীবন্ত ও ধারাবাহিক স্বপ্ন জাগিয়ে তোলা”
প্রথম অধ্যায়ে যে “ফিকশনাল ড্রিম” এর কথা এসেছে, তার ওপর এই অধ্যায়ে গার্ডনার বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, গল্পের ভিত তৈরি হয় স্পষ্ট ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রের মাধ্যমে—চরিত্রদের আচরণ, দৃশ্যপটের রং-রূপ, শব্দ, গন্ধ—সবকিছু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে পাঠকের মনে যেন গল্পের দুনিয়া বাস্তব হয়ে ওঠে।
লেখকের দায়িত্ব হলো সামঞ্জস্য বজায় রাখা; একটি সামান্য ভুল তথ্য, উচ্চারণগত ত্রুটি, বা অযাচিত শৈলীর পরিবর্তন পাঠককে সেই স্বপ্ন থেকে টেনে বের করে আনতে পারে। গার্ডনার দৃঢ়ভাবে বলেন, বাস্তবতা এবং গল্পের অভ্যন্তরীণ চুক্তি (যেমন টাইম-ফ্রেম, চরিত্রের আচরণ, ভাষিক টোন) সবসময় মেনে চলতে হবে।
তিনি সংক্ষেপ (summary) ও দৃশ্যপট (scene)-এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার কথাও উল্লেখ করেন। টানা সংক্ষেপ সহজে গল্পের আবেগ ধরে রাখতে পারে না, কারণ সেটি পাঠকের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে সীমিত করে। অন্যদিকে, দৃশ্য বা সিন “উন্মুখ বাস্তবতা” নিয়ে আসে—সংলাপ, কর্ম, আবেগের সরাসরি মঞ্চায়ন—যা পাঠককে গভীরে নিয়ে যায়। লেখককে দুইয়ের সুষম মিশ্রণ ঘটিয়ে গল্পের ছন্দ বজায় রাখতে হয়।
অধ্যায় ৬: “প্রতিফলন”
এই অধ্যায়ে গার্ডনার গল্পের মধ্যে “প্রতিফলন” বা রেফ্লেকশনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন—যে মুহূর্তে বর্ণনাকারী বা চরিত্ররা ঘটা ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করে। এটা গল্পে “মনের চোখ” খুলে দেওয়ার মতো, যেখানে আবেগ, অভিজ্ঞতা এবং নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।
তবে অনেক প্রতিফলন গল্পের গতি কমিয়ে দেয়, আর পাঠককে গল্পের স্বপ্ন থেকে আলগা করে ফেলতে পারে। গার্ডনার এখানে পরিমিতিবোধের ওপর জোর দেন—প্রতিফলন যেন গল্পের প্রয়োজনে আসে, যাতে বিরতি নিয়ে পাঠক ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু কখনোই উপদেশ বা লেকচারের মতো হয়ে না দাঁড়ায়।
সেরা প্রতিফলন সেই যা চরিত্রের বাস্তব প্রয়োজন বা কৌতূহল থেকে আসে। উদ্দেশ্যহীন বা পরিকল্পনাহীন আত্মকথন কেবলই গল্পের কাণ্ডকীর্তিকে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং, লেখককে দেখতে হবে প্রতিটি প্রতিফলন আসলে গল্পকে কতটুকু সমৃদ্ধ করছে, না কি শুধুই গতি কমাচ্ছে।
অধ্যায় ৭: “থিম, বৈচিত্র ও নীতিশিক্ষামূলক ঝুঁকি”
এই অধ্যায়ে গার্ডনার থিম বা মূল ভাবনার গঠন এবং “Didacticism” বা নীতিশিক্ষামূলক হয়ে ওঠার ঝুঁকি নিয়ে কথা বলেন। কথাসাহিত্য তার স্বাভাবিক প্রবণতায়ই নৈতিক ও দার্শনিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। কিন্তু এই থিম লেখকের হৃদয় ও চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকে জন্ম নিলে সেটি শক্তিশালী হয়। সরাসরি প্রচারমূলক বা “নীতিকথা” পাঠককে সংযোগহারী করে তুলতে পারে।
গার্ডনার “variation” বা বৈচিত্রের কথা বলেন। গল্পে বা উপন্যাসে কোনো প্রতীক, দৃশ্য বা আইডিয়াকে বিভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি করা—কখনো স্পষ্টভাবে, কখনো আভাসে—গল্পের কেন্দ্রীয় থিমকে জোরদার করতে পারে। এটি গল্পে সুর ও অনুরণন আনে। কিন্তু এই পুনরাবৃত্তি যদি প্রকাশ্যে ধ্বনিত হয়—অর্থাৎ লেখক পাঠককে দাঁড় করিয়ে ব্যাখ্যা দেন—তবে গল্পের স্বপ্ন ভেঙে যেতে পারে।
গার্ডনার মনে করিয়ে দেন, গল্পের থিম উত্তীর্ণ হয় যখন সেটি নীতিবাক্য হয়ে না দাঁড়িয়ে চরিত্র, ঘটনাপ্রবাহ ও পরিণতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। থিমকে কখনোই কৃত্রিমভাবে আরোপ করা উচিত নয়; বরং সেটি টেক্সটের অন্তর্গত বাস্তবতা থেকে ফুঁটে উঠবে এবং পাঠককে ভাবতে উদ্দীপিত করবে।
অধ্যায় ৮: “প্রতীক”
প্রতীক হলো এমন কোনো বস্তু, চিত্র বা ঘটনা যা আক্ষরিক তাৎপর্যের বাইরে গিয়ে প্রসারিত অর্থ বহন করে। গার্ডনার বলেন, প্রতীক কথাসাহিত্যের সবল হাতিয়ার, তবে পরিমিত ও দক্ষ ব্যবহারে এর শক্তি ফুটে ওঠে। স্পষ্ট বা জোরপূর্বক প্রতীকায়ন গল্পের স্বাভাবিকতাকে ব্যাহত করতে পারে।
তিনি দুই ধরনের প্রতীকের কথা উল্লেখ করেন: “স্বেচ্ছাচারী প্রতীক” (arbitrary symbol) ও “জৈবিক প্রতীক” (organic symbol)। স্বেচ্ছাচারী প্রতীক গল্পের বিষয়বস্তুর সাথে সহজাত সংযোগ না থাকায় শুধু লেখকের ইচ্ছেমতো বসানো মনে হতে পারে। আর জৈবিক প্রতীক গল্পের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা, চরিত্রের অভ্যাস বা ঘটনার ধারাবাহিকতা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম নেয়। একটি চরিত্রের খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিস, বা কোনো প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য যা বারবার আসে ও আবেগকে প্রতিফলিত করে—তা হয়ে উঠতে পারে জৈবিক প্রতীক।
লেখককে আহবান করা হয় সচেতন থাকতে, যেন প্রতীকের ব্যবহার গল্পের গূঢ় অর্থ ও আবেগকে আরও দৃঢ় করে তোলে, কিন্তু কখনোই মূল গল্পের উপর চাপে পরিণত না হয়।
অধ্যায় ৯: “লেখকের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা”
এই অধ্যায়ে গার্ডনার লেখক হিসেবে পরিপক্ক হয়ে ওঠার পথনির্দেশ দেন। তিনি বলেন, বহুমুখী ও গভীর পাঠাভ্যাস আবশ্যিক। বিভিন্ন শৈলী, যুগ ও সংস্কৃতির সাহিত্য পড়লে লেখক তার নিজের রচনাশৈলীর পরিধি প্রসারিত করতে পারেন।
গার্ডনার ফর্মাল শিক্ষার গুরুত্বকেও স্বীকার করেন—লেখালিখির কর্মশালা, সেমিনার, বা সৃজনশীল লিখন-সংক্রান্ত ডিগ্রি প্রোগ্রাম। তবে এগুলোই একমাত্র উপায় নয়। কেউ চাইলে একান্ত অনুশীলন ও নিয়মতান্ত্রিক পাঠচর্চার মাধ্যমে একই দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। লেখককে লাগাতারভাবে ব্যর্থ খসড়া ও খোঁজাখুঁজি থেকে শিখে যেতে হবে; এটি স্থির ও অনন্ত প্রক্রিয়া।
এছাড়া লেখককে যথেষ্ট বাস্তবজ্ঞান ও নৈতিক-মানসিক পরিপক্কতা অর্জন করতে হবে। জীবনকে যত নিবিড়ভাবে দেখা যায়, অভিজ্ঞতা ও নৈতিক ভাবনা যত গভীর হয়, লেখায় তত বেশি সত্য ও অনুরণন ফুটে ওঠে। কেবল ভঙ্গিমা বা শব্দকৌশল দিয়ে বড় সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়; দীর্ঘ অনুশীলন, পর্যবেক্ষণ ও মানবিক বোধই লেখককে তার সেরা সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যায়।
অধ্যায় ১০: “বিশ্বাস”
পুস্তকের প্রথম ভাগের শেষ অধ্যায়ে গার্ডনার লেখকসত্তার “বিশ্বাস” নিয়ে আলোচনা করেন—লেখকের নিজের ওপর বিশ্বাস এবং কথাসাহিত্যের সামাজিক-মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাস। সাহিত্যিক স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থাকলেও বাস্তবিক পেশাগত চাহিদা বা প্রকাশনার বাজার-চাপে অনেকেই নিরুৎসাহিত হতে পারেন। কিন্তু গার্ডনারের মতে, সত্যিকারের লেখক সেই ব্যক্তি যিনি নিজের ভেতরে দৃঢ়চেতা আত্মবিশ্বাস ধারণ করেন যে এই গল্প বলা দরকার, এবং এটি মানুষকে নাড়া দিতে সক্ষম।
এই বিশ্বাস একাধিক স্তরে কাজ করে—নিজের সৃষ্টির মূল্য বিষয়ে আস্থা রাখা, গল্পের শক্তিতে আস্থা রাখা, এবং ভাবনা ও শব্দের মধ্য দিয়ে মানবিক সত্যকে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় আস্থা রাখা। আর্থিক সাফল্য কিংবা পরিচিতি আসতে সময় লাগতে পারে; কিন্তু লেখকের প্রকৃত প্রেরণা হতে হবে অনুরাগ ও গভীর তাগিদ—“যে গল্পটা না বললে নয়” সেই বোধ।
অধ্যায় ১১: “কারিগরি বিবেচনা ও অনুশীলন (দ্বিতীয় ভাগের সূচনা)”
দ্বিতীয় ভাগে গার্ডনার আরও ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক আলোচনা শুরু করেন। এই অধ্যায়ে তিনি লেখকদের জন্য বিভিন্ন রকমের অনুশীলন বা এক্সারসাইজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। গার্ডনার বলেন, একজন সঙ্গীতশিল্পী যেমন নিয়মিত গামুট (scales) অনুশীলন করেন, তেমনি লেখককেও ছোট ছোট অনুশীলনের মাধ্যমে হাত পাকাতে হবে।
এই অনুশীলনগুলো বিষয়ভিত্তিক হতে পারে—যেমন: সংবেদী বর্ণনা (descriptive passages), সংলাপ লেখা, দৃশ্যের গঠন, দৃষ্টিকোণ বদলানোর কৌশল, প্রতীক ব্যবহার ইত্যাদি। এসব অনুশীলন বেশি সময়ে বড় গল্পে না গিয়ে নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হয়।
তিনি সতর্ক করেন যে শুধু এসব অনুশীলন করলেই হবে না; সেগুলো থেকে শেখা কৌশলগুলো গল্প-উপন্যাসে প্রয়োগ করার ক্ষমতাও অর্জন করতে হবে। অনুশীলনে বারবার ভুল করা, সেগুলো শোধরানো, এবং তবেই লেখক তার শৈলী ও দক্ষতার বিস্তার ঘটাতে পারবেন।
অধ্যায় ১২: “দৃশ্য নির্মাণ”
গল্পের অন্যতম মৌলিক কাঠামো হল “দৃশ্য” বা সিন। গার্ডনার বলেন, একটি দৃশ্যের মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো পরিবর্তন বা দ্বন্দ্বকে সরাসরি মঞ্চায়ন করা—চরিত্রদের সংলাপ, বিবরণ, গতিবিধি ইত্যাদির মাধ্যমে। দৃশ্য ছাড়া গল্প যেমন প্রাণ পায় না, তেমনি দৃশ্যগুলোর সার্বিক মিথস্ক্রিয়ায়ই গল্প এগিয়ে যায়।
লেখককে বুঝতে হবে কখন সংলাপ বাড়াতে হবে, কখন বর্ণনা সংযত রাখতে হবে, কখন চরিত্রদের মধ্যে টানাপড়েনকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সংলাপ যেন এক্সপোজিশনের সরল বাহন না হয়ে যায়; বরং চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, আবেগ ও গোপন উদ্দেশ্যের স্ফূরণ ঘটায়। বর্ণনা যেন শুধু স্থান-কাল-পরিবেশ সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ না থাকে; সেটি আবহ ও অর্থবহ হয়ে উঠতে হবে।
গার্ডনার আরও বলেন, দৃশ্য নির্মাণে দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের ব্যাপারে সতর্কতা দরকার। হঠাৎ করে POV (point of view) বদলে গেলে পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। তাই অবস্থান বদলের আগে গল্পের সামগ্রিক ঐক্য ও ধারাবাহিকতা মাথায় রাখতে হবে। একটি দৃশ্য কীভাবে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার “মহৎ কারণ” লেখককেই আগে স্পষ্ট করতে হবে।
অধ্যায় ১৩: “বাক্য, ভাষা ও শৈলী”
এই অধ্যায়ে গার্ডনার ভাষা ব্যবহারের মৌলিক কাজ—বাক্যগঠন—নিয়ে বিস্তারিত বলেন। প্রতিটি বাক্য হলো কথাসাহিত্যের মূল ইউনিট; সঠিক গতির জন্য, স্বরের জন্য, অর্থের স্পষ্টতার জন্য বাক্যগঠনে যত্নবান হওয়া জরুরি। ছোট-বড় বাক্যের সমন্বয়, ভিন্ন রূপের বুনন, শব্দচয়নের মৌলিকত্ব—এসবই রচনাকে গতিময় ও প্রাণবন্ত করে।
গার্ডনার লেখকদের সতর্ক করেন যে স্রেফ “জটিল” শব্দ বা “অলঙ্কৃত” বাক্য ব্যবহার করলেই শৈলী প্রতিষ্ঠা হয় না। বরং যেখানে যে নির্দিষ্ট শব্দ প্রয়োজন, সেটি আনতে পারাই আসল দক্ষতা। শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, তবে তা যেন বাড়াবাড়ি বা দেখানোর জন্য না হয়।
লেখকের ব্যক্তিগত শৈলী মূলত উঠে আসে তার বাক্যগঠন, দৃষ্টিকোণ এবং আখ্যানকেন্দ্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে। শৈলী গল্পকে যে আবহ ও অর্থ দিতে চায়, সেটিকে স্পষ্টভাবে ধারণ করতে হবে। সমসাময়িক বা ঐতিহাসিক—যে কোনো রচনাতেই, ভাষা ও শৈলীর ভারসাম্য পাঠকের কাছে গল্পের আবেগকে পৌছে দেওয়ার বড় উপায়।
অধ্যায় ১৪: “পুনর্লিখন: ভাস্করের কাজ”
গার্ডনারের মতে, “রিভিশন” বা পুনর্লিখন কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ঠিক যেন ভাস্করের নিপুণ কাজের মতো। মূল খসড়া হলো পাথরের মতো; লেখককে বহু পর্যায়ে ঘষে-মেজে, টুকরো ফেলে দিয়ে বা নতুন করে যুক্ত করে গল্পটিকে তার চূড়ান্ত রূপ দিতে হয়।
তিনি বলেন, লেখকদের উচিত একটি খসড়া লিখে কিছুদিন সেটি দূরে রাখা, যাতে পরবর্তীতে নিরপেক্ষ চোখে দেখা যায় কোথায় ভুল, কোথায় উৎকৃষ্ট সম্ভাবনা। গার্ডনার অভিজ্ঞ পাঠক বা আস্থাভাজন বন্ধুর মতামত নেওয়ার পরামর্শ দেন, তবে সেই মতামতও যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করতে হবে।
পুনর্লিখনে বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন—চরিত্র বাদ দেওয়া, সংলাপ পুনর্লিখন, প্লটের সারি বদলে দেওয়া—সম্ভব। ছোট খুঁটিনাটি—শব্দ নির্বাচন, যতি-চিহ্ন, সংলাপের সূক্ষ্ম টান—সবই পাশাপাশি চলে। বাস্তবে, এই পুনর্লিখনই হলো লেখকের সত্যিকারের কারিগরি চর্চা, যেখানে অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণার মিলনে গল্পটি পরিপূর্ণতা পায়।
অধ্যায় ১৫: “উন্নতির জন্য অনুশীলন”
গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে গার্ডনার একগুচ্ছ স্পেসিফিক অনুশীলনের কথা বলেন, যা লেখকদের গল্প বলার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কখনো এটা হতে পারে একই দৃশ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, কখনোবা কেবল সংলাপ দিয়ে একটি ঝগড়া বা দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলা।
কিছু অনুশীলন কেন্দ্রীভূত হয় নির্দিষ্ট কারিগরি দক্ষতার ওপর—যেমন POV পরিবর্তন ছাড়াই দৃশ্যের আবেগী উত্তাপ বাড়ানো, যেকোনো বস্তুকে প্রতীকের স্তরে নিয়ে যাওয়া, বা ব্যতিক্রমী গদ্যশৈলী ব্যবহার করা। আবার কিছু অনুশীলন লেখকদের অচেনা থিম বা অচেনা চরিত্র নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ দেয়, যেন সৃজনশীল পরিসর প্রশস্ত হয়।
গার্ডনার মনে করিয়ে দেন যে এই অনুশীলনগুলোর লক্ষ্য শুধু একটি নিখুঁত গল্প লেখা নয়; বরং ক্রমাগত চেষ্টা ও পরীক্ষার ভেতর দিয়ে ভাষা ও কাঠামো নিয়ে লেখকের দক্ষতা উন্নীত করা। প্রতিটি ব্যর্থ বা অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টাও ভবিষ্যতের সফল গল্প লেখার পাথেয় হতে পারে।
জন গার্ডনারের The Art of Fiction নবীন ও পেশাদার উভয় ধরনের লেখকদের জন্যই এক অনন্য সমন্বিত গাইড। তিনি সার্বিকভাবে জোর দেন একটি “জীবন্ত ও ধারাবাহিক স্বপ্ন” তৈরির দিকে, যেখানে পাঠক গল্পের ভেতর ডুবে যাবেন এবং আবেগ ও বুদ্ধি—উভয় দিক থেকেই তৃপ্ত হবেন। এ জন্য লেখককে ভাষার সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ, নান্দনিক সততা এবং গভীর মানবিক উপলব্ধি অর্জন করতে হবে।
গার্ডনার দেখিয়ে দেন যে লেখার কৌশল—বাক্যগঠন, দৃশ্যায়ন, প্রতীক, থিম—এসবই আসলে গল্পের স্বপ্নটিকে সত্যিকার বাস্তবতায় গড়ে তোলার পথ। পাশাপাশি, লেখকের নিজের জীবনীশক্তি, অভিজ্ঞতা ও নৈতিক চেতনা গল্পের কেন্দ্রে প্রাণ সঞ্চার করে।
অবশ্যই পড়া ও অনুশীলন—এই দুই প্রক্রিয়া কখনো শেষ হয় না। ভাষা ও কল্পনাশক্তিকে শাণিত করার জন্য গার্ডনারের দেওয়া অনুশীলনগুলো নিয়মিত চর্চা করতে হবে। স্বতন্ত্র স্বর তৈরি করতে লেখককে বহুদিনের শ্রম ও সততার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই বইয়ের মূল তাৎপর্য এখানেই—লেখককে সামগ্রিকভাবে অনুপ্রাণিত করা এবং প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ হতে সাহায্য করা, যাতে শেষ পর্যন্ত লেখার মধ্যে ধরা পড়ে জীবনের ভিন্ন মাত্রা এবং পাঠকের মনে জাগে মানবীয়, নীতিগত ও শিল্পসৌন্দর্যের অতলস্পর্শী অনুভূতি।