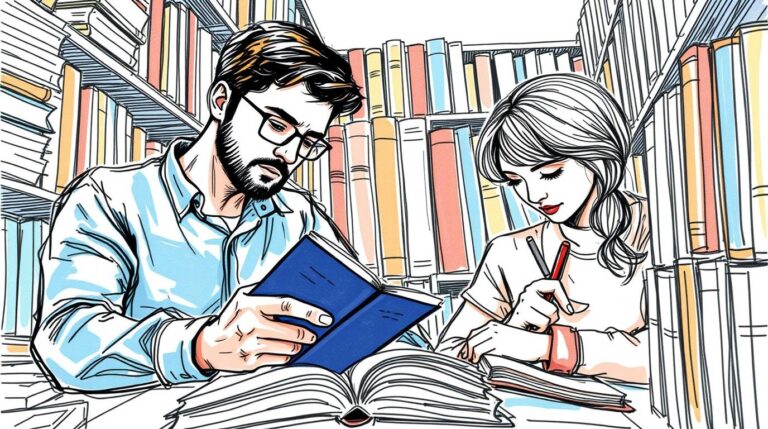Steering the Craft: A Twenty-First-Century Guide to Sailing the Sea of Story
Book by Ursula K. Le Guin
উরসুলা কে. লে গুইনের Steering the Craft: A Twenty-First-Century Guide to Sailing the Sea of Story লেখালেখির শিল্প সম্পর্কে এক অনুপ্রেরণাদায়ক, ব্যবহারিক ও গভীর পর্যালোচনা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮ সালে, পরবর্তী সংস্করণটি ২০১৫ সালে আপডেট করা হয়, যাতে একবিংশ শতাব্দীর প্রকাশনা পরিবেশ, পাঠাভ্যাস এবং লেখকদের প্রয়োজনের পরিবর্তনগুলোকে বিবেচনা করা যায়। লে গুইন তাঁর লেখাকে এক ধরনের সমুদ্রযাত্রার সঙ্গে তুলনা করেছেন: ভাষা হলো সেই জাহাজ, কাহিনি হলো ভ্রমণপথ, আর লেখক হলেন নাবিক বা ক্যাপ্টেন। শুদ্ধ ও অনড় বিধিনিষেধের তালিকা দেওয়ার বদলে, তিনি লেখালেখির নানা দিক অন্বেষণ করার প্রস্তাব দেন—স্টাইল, কণ্ঠস্বর (ভয়েস), দৃষ্টিকোণ (পয়েন্ট অব ভিউ), ভাষার সুর-ছন্দ ইত্যাদি কেমনভাবে লেখা ও পাঠকে সমৃদ্ধ করে তা ব্যাখ্যা করেন।
অনেক লেখালেখির গাইড বই কাহিনি-কাঠামো, চরিত্র কিংবা থিম দিয়ে শুরু করে। কিন্তু লে গুইন লেখার অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেন: ব্যাকরণগত নিয়ম শিখে নেওয়াই মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং ভাষার দ্যোতনা ও সুরকে উপলব্ধি করা। তাঁর বিশ্বাস, সঠিক রীতিনীতি জানা সৃষ্টিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করে না; বরং লেখক-মননকে আরও শানিত করে। প্রতিটি অধ্যায়ে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট স্টাইলিস্টিক বিষয় আলোচনা করা হয়, ক্লাসিক সাহিত্য থেকে উদাহরণ দেওয়া হয়, এবং সেইসঙ্গে কিছু অনুশীলনী বা অনুপ্রেরণামূলক “গেম” দেওয়া হয়। লেখার স্বর বরাবরই বন্ধুত্বপূর্ণ, কিন্তু তিনি লেখকদের যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেন—যাতে ভাষার জাদুকে ধরে রেখে কারিগরি দক্ষতাও অর্জন করা যায়।
বইয়ের পাতায় পাতায় লে গুইন লেখকদের পথ দেখান: বর্ণনা (ন্যারেটিভ) ও শব্দচয়নের (ডিকশন) সূক্ষ্ম ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে লয় ও ছন্দ তৈরি করা যায়, কেমনভাবে পুনরাবৃত্তি (রিপিটিশন) ও বাক্যগঠন (সিনট্যাক্স) আখ্যানকে আরও প্রভাবশালী করে তুলতে পারে, বা কোন পদ্ধতিতে দৃষ্টিকোণ ও সময়ের গতি-প্রকৃতি (পেসিং) পরিচালিত করা যায়। গ্রন্থটির সারমর্মে দেখা যায়, লেখালেখিকে তিনি একটি যাত্রা হিসেবেই দেখছেন। এর জন্য চাই দক্ষতা ও নিষ্ঠা—লেখককে বাহন হিসেবে ভাষার ওপর আস্থা রাখতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে গল্পের সম্ভাব্য সব দিক খোলা রাখতে হবে।
অধ্যায় ১: আপনার লেখার ধ্বনি
এই অধ্যায়ে লে গুইন শব্দের ধ্বনি বা “সাউন্ড”–এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বহু লেখালেখির পুস্তক কাহিনি, চরিত্র বা থিম দিয়ে শুরু করে, কিন্তু লে গুইন ইচ্ছাকৃতভাবে লয় ও সুর বা “রিদম অ্যান্ড টোন” দিয়ে আলাপ শুরু করেন। তাঁর যুক্তি হলো, গদ্য কেবল পড়া হয় না, মানসচোখের সঙ্গে সঙ্গে মানসকর্ণেও ধ্বনিত হয়; শক্তিশালী লেখার প্রাথমিক গুণ হলো সেটির স্পষ্ট ছন্দ।
লে গুইন বলেন, প্রতিটি লেখার কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র হোক—এটিই কাম্য। ভাষা নিজেই একধরনের সুরময়ত্ব বয়ে আনে; ছোট ও বড় শব্দের বিন্যাস, দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত বাক্যের ছন্দ, বিরামচিহ্নের (পাংচুয়েশন) প্রয়োগ—সবকিছু মিলিয়ে গদ্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে। ঘরোয়া দৃশ্য হোক বা রোমাঞ্চকর যুদ্ধের দৃশ্য—সঠিক ছন্দ এনে দেওয়া পাঠকদেরকে ঘটনাপ্রবাহে মগ্ন করে।
এই অধ্যায়ে এক গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস হলো উচ্চস্বরে পড়া। লে গুইন জোর দিয়ে বলেন, লেখকরা যেন তাঁদের লেখা নিজেরা জোরে পড়েন, বা অন্য কারওকে পড়ে শোনান। এতে করে বাক্যের ছন্দ ও বাধাগুলো স্পষ্ট শোনা যায়। উচাটন শব্দচয়ন, সামঞ্জস্যহীন দীর্ঘ বাক্য, বা বিরামচিহ্নের ভুল প্রয়োগ সহজে ধরা পড়ে। শব্দের অভ্যন্তরীণ সুরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে একজন লেখক অনুভব করতে পারেন কোন অংশগুলো ‘পড়তে’ বা ‘শুনতে’ ভাল লাগছে, আর কোথায় সমস্যা রয়ে গেছে।
অধ্যায়ের শেষে লে গুইন একটি সংক্ষিপ্ত অনুশীলনী রাখেন, যেখানে লেখকদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে যে, গল্পের যৌক্তিক কাঠামোর চিন্তা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ধ্বনি বা সুরের ওপর মনোযোগ দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করতে। এই অনুশীলন লেখকদের “ইয়ার” বা শ্রবণেন্দ্রিয়কে আরও সূক্ষ্ম করে তুলতে সাহায্য করে।
অধ্যায় ২: বিরামচিহ্ন ও ব্যাকরণ
আগের অধ্যায়ে ধ্বনি ও ছন্দের প্রসঙ্গ ছিল; এখন লে গুইন একটু বেশি কারিগরি দিক—বিরামচিহ্ন ও ব্যাকরণ—নিয়ে কথা বলেন। অনেকেই ব্যাকরণকে “নীরস” মনে করেন, বা বিরামচিহ্নকে তুচ্ছ মনে করে এড়িয়ে যেতে চান। কিন্তু লে গুইন মনে করিয়ে দেন যে, বিরামচিহ্ন ছাড়া স্পষ্টতা ও ছন্দ, দুটোই ফিকে হয়ে যায়। বিরামচিহ্ন আসলে পাঠকের চোখ ও মনে গতি নির্ধারণ করে।
তিনি নিয়মিত ভুলগুলোর মধ্যে গ্রামাটিকাল পয়েন্ট, যেমন রানের বাক্য (run-on sentences), কমা স্প্লাইস, সেমিকোলনের অপব্যবহার ইত্যাদি আলোচনা করেন। শুষ্কভাবে উপদেশ দেওয়ার বদলে তিনি দেখান কীভাবে সচেতনভাবে বিরামচিহ্নের ব্যবহার লেখার ছন্দ ও অর্থের সূক্ষ্মত্ব বাড়িয়ে তোলে। একটি সঠিক জায়গায় কমার ব্যবহার পাঠকের মনে স্বল্প বিরতি তৈরি করে, যা উত্তেজনা বা ভাবগম্ভীরতা জাগিয়ে তুলতে পারে। আবার অন্য জায়গায় একটি ড্যাশ (—) কোনো বিষয়কে আলাদা করে গুরুত্ব দিতে পারে।
ব্যাকরণ প্রসঙ্গে লে গুইন বলেন, লেখককে প্রথাগত নিয়ম জানতে হবে, যাতে দরকার হলে তা সৃজনশীলভাবে ব্যবহার বা বিকৃত করা যায়। সংলাপের ক্ষেত্রে সচেতনভাবে ব্যাকরণ-বিকৃতি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলতে পারে। তবে নিয়ম না জানলে তা ভুলে পর্যবসিত হতে পারে।
এই অধ্যায়ের শেষাংশে তিনি সংক্ষিপ্ত একটি অনুশীলনী দেন—যেখানে মূলত সংলাপ লিখে চিহ্নিত করতে হবে, কীভাবে বিরামচিহ্ন এবং ব্যাকরণ চরিত্রের আবেগ বা দৃশ্যের গতিকে প্রভাবিত করে। এতে লেখকরা উপলব্ধি করতে পারেন যে, ব্যাকরণ ও বিরামচিহ্ন শুধু বানান-সংশোধন নয়, এটি লেখার সুরের স্থপতি।
অধ্যায় ৩: বাক্যের দৈর্ঘ্য ও জটিল গঠন
এই অধ্যায়ে লে গুইন বাক্যগঠন নিয়ে আরও বিস্তারে যান: কীভাবে বাক্যের দৈর্ঘ্য ও গঠন পাঠকের অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে। তাঁর কথা হলো, বাক্য কেবল তথ্য সরবরাহের বাহন নয়—এটি এককভাবে গতির বা ছন্দের অনুভূতি তৈরি করে এবং পাঠের আনন্দ বা ক্লান্তি নীয়ন্ত্রণ করে।
লে গুইন ব্যাখ্যা করেন যে সংক্ষিপ্ত, সরল বাক্য তীক্ষ্ণতা ও দ্রুততা জাগিয়ে তুলতে পারে, অন্যদিকে দীর্ঘ, জটিল বাক্য পাঠককে এক গভীর ঘোরের মধ্যে নিয়ে যায় বা ধীর ভাবনায় ডুবিয়ে রাখে। কোনটি ভালো বা খারাপ, তা নির্ভর করে দৃশ্য বা আখ্যানের প্রয়োজনে। উদাহরণ হিসেবে তিনি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সংক্ষিপ্ত বাক্যের সাথে ভার্জিনিয়া উল্ফ বা গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের দীর্ঘ, প্রবাহমান বাক্যের তুলনা টানেন।
অতিরিক্ত জটিল বাক্য ব্যবহারের ঝুঁকি নিয়ে তিনি সতর্ক করেন: এক বাক্যে অন túl বেশি তথ্য দিলে পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে খুব ছোট ছোট বাক্যের ধারাবাহিক ব্যবহার পাঠকে খাপছাড়া বা বিক্ষিপ্ত মনে হতে পারে। তাই ব্যালান্স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
এই অধ্যায়ের অনুশীলনীতে তিনি লেখকদের দুটি অংশ লিখতে বলেন—একটি অংশ খুব ছোট বাক্যের সমন্বয়ে, আরেকটি অংশে অন্তত একটিমাত্র দীর্ঘ বাক্য থাকবে। উদ্দেশ্য হলো বাক্যের দৈর্ঘ্য ও গঠনের বৈচিত্র বুঝে উঠা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কীভাবে তা প্রয়োগ করা যায় তা অনুধাবন করা।
অধ্যায় ৪: পুনরাবৃত্তি
অনেক লেখালেখির গাইড বই বলে, কাছাকাছি শব্দ বা বাক্যাংশ পুনরায় ব্যবহার করা ঠিক নয়, কারণ এটি “খারাপ লেখা” নির্দেশ করে। কিন্তু লে গুইন এখানে পুনরাবৃত্তি নিয়ে একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করেন। তিনি বলেন, হঠাৎ করে অনর্থক বা অসাবধানতায় একই শব্দ ও ফ্রেজ বারবার ব্যবহার লেখার মান নিচে নামাতে পারে, তবে সচেতনভাবে নির্বাচিত পুনরাবৃত্তি গল্পের কাঠামোকে শক্তিশালী বা শিল্পিত করে তুলতে পারে।
পুনরাবৃত্তি কীভাবে ছন্দ ও অনুরণন তৈরি করে, লে গুইন তা ব্যাখ্যা করেন। গল্পের নির্দিষ্ট ভাবনা বা চরিত্রের মনোবাসনার প্রতিফলন হিসেবে পুনরাবৃত্ত শব্দ বা বাক্যাংশ পাঠকের মনে গভীর ছাপ ফেলতে পারে। কবিতায় এটি সাধারণত বেশি দেখা যায়। গদ্যেও, সঠিকভাবে ব্যবহৃত পুনরাবৃত্তি আখ্যানের ভেতর এক ধরনের মন্ত্রোচ্চারণের আবেশ অথবা সংকটের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
তবে সেইসঙ্গে অপ্রয়োজনীয় বা অনিচ্ছাকৃত পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে তিনি লেখকদের সতর্ক করেন। বিশেষ করে “just,” “very,” “actually” ইত্যাদি সহায়ক বা গতানুগতিক শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হলে লেখার শক্তি কমে যায়।
এই অধ্যায়ের অনুশীলনীতে তিনি লেখকদের অনুরোধ করেন সচেতনভাবে একটি অংশ লিখতে, যেখানে পুনরাবৃত্তি মূল অলঙ্কারিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন তা বিরক্তিকর না হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমে লেখকেরা উপলব্ধি করতে পারেন কখন পুনরাবৃত্তি শিল্পিত, আর কখন তা আখ্যানের ছন্দে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।
অধ্যায় ৫: বিশেষণ ও ক্রিয়া–বিশেষণ
এই অধ্যায়ে লে গুইন বিশেষণ (Adjective) ও ক্রিয়া–বিশেষণ (Adverb) নিয়ে আলোচনা করেন, যেগুলো সাধারণত “অতিরিক্ত” বা “সহায়ক” শব্দ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, মার্ক টোয়েনের বিখ্যাত বাণী ছিল “Kill your adverbs”—ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবহার না করাই শ্রেয়। তবে লে গুইন একে সরাসরি নিষিদ্ধ করতে বলেন না; বরং তিনি দেখান, প্রায়ই এগুলোকে দুর্বল ক্রিয়া বা দুর্বল বিশেষ্যকে (noun) ঢেকে দিতে ব্যবহার করা হয়।
লে গুইনের মূল কথা হলো, যদি শক্তিশালী ক্রিয়া বা বিশেষ্য পাওয়া যায় তবে আলাদা বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণের প্রয়োজন পড়ে না। যেমন “walked slowly”-এর বদলে “shuffled,” “crept,” অথবা “meandered” ব্যবহারে একটি শব্দেই দৃশ্য ও ভাব দুটোই স্পষ্ট হয়। একইভাবে “stunningly red”-এর বদলে “crimson” শব্দটি সেই তীব্রতা-সমৃদ্ধ বর্ণনা দিতে পারে।
তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই পরামর্শ নিঃশর্ত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ লেখার ছন্দ ঠিক রাখতে কিংবা সূক্ষ্ম তাৎপর্য বা আবেগ প্রকাশ করতে অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। মূল কথা হলো সচেতন ও পরিমিত ব্যবহার। দুর্বল শব্দচয়নের ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার চেয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্বাচিত বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ প্রভাববিস্তারী হয়ে উঠতে পারে।
অনুশীলনীতে তিনি লেখকদেরকে আহ্বান করেন একটি লেখা থেকে সব বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ বাদ দিতে, এবং সেগুলোকে প্রয়োজন হলে আরও নির্দিষ্ট বা শক্তিশালী ক্রিয়া ও বিশেষ্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে। তারপর যা একেবারেই অপরিহার্য মনে হয়, সেগুলো পুনরায় যুক্ত করতে। এতে লেখকরা বুঝতে শিখবেন কোন বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ আসলেই জরুরি, আর কোনটি “অতিরিক্ত”।
অধ্যায় ৬: দৃষ্টিকোণ (পয়েন্ট অব ভিউ) ও কণ্ঠস্বর (ভয়েস)
দৃষ্টিকোণ বা পয়েন্ট অব ভিউ হলো আখ্যানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এখানে লে গুইন প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ এবং তৃতীয় পুরুষ (নানা মাত্রায়) দৃষ্টিকোণকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখান যে, দৃষ্টিকোণ কেবল কাহিনিতে তথ্য পরিবেশনের পদ্ধতি নয়—এটি কণ্ঠস্বর, স্বর, ভঙ্গি ও আবেগের অভিজ্ঞতায় বড় ভূমিকা রাখে।
লে গুইন মূলত তিনটি শ্রেণিতে দৃষ্টিকোণ ভাগ করেন:
- প্রথম পুরুষ (First Person): গল্প যে-চরিত্র বা “আমি” বলছে, তার দৃষ্টিকোণ। এটি পাঠকের কাছে চরিত্রটির অনুভূতি, চিন্তা খুব নিবিড়ভাবে পৌঁছে দেয়। তবে narrator অন্য কোথাও উপস্থিত না থাকলে সেসব ঘটনা সরাসরি দেখানো কঠিন হতে পারে।
- দ্বিতীয় পুরুষ (Second Person): এক্ষেত্রে গল্পে পাঠক বা কোনো কাল্পনিক “তুমি” চরিত্রকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়। এটি খুবই আকস্মিক ও immersive অভিজ্ঞতা দিতে পারে, কিন্তু অল্পতেই কৃত্রিম বা বিভ্রান্তিকর লাগতে পারে যদি খুব যত্ন করে না লেখা হয়।
- তৃতীয় পুরুষ (Third Person):
- সর্বজ্ঞ (Omniscient): এখানে বর্ণনাকারী সবকিছু জানে, চরিত্রদের অন্তর্লোকসহ। এটি বড় পরিসরের বা মহাকাব্যিক গল্পের জন্য উপযোগী। তবে ভুলভাবে ব্যবহার করলে পাঠক থেকে একধরনের দূরত্ব তৈরি হতে পারে।
- সীমিত (Limited): এক বা কিছু চরিত্রের চিন্তা ও দৃষ্টিকোণেই গল্প সীমিত থাকে। এতে নির্দিষ্ট চরিত্রের গভীরতা বাড়ে, কিন্তু অন্য চরিত্রদের ভাবনা বা ঘটনা জানার সুযোগ সরাসরি থাকে না।
এরপর তিনি দেখান কীভাবে কণ্ঠস্বর (Voice)—লেখার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব—দৃষ্টিকোণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সর্বজ্ঞ বর্ণনা হতে পারে কিছুটা বাস্তব থেকে দূরে, অলঙ্কৃত বা প্রাচীন-ধাঁচের। অন্যদিকে প্রথম পুরুষ হলে চরিত্রের নিজস্ব উচ্চারণ, শব্দচয়ন, এমনকি ভাবুক স্বভাবের পরিচয়ও স্পষ্ট হয়।
অধ্যায়ের অনুশীলনীতে একজন লেখককে একই দৃশ্য প্রথম পুরুষে ও তৃতীয় পুরুষে লিখতে বলেন। যাতে বোঝা যায়, কীভাবে দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করলে গল্পের আবেদন, কণ্ঠস্বর ও তথ্যপ্রবাহ পরিবর্তিত হয়।
অধ্যায় ৭: দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সাধারণ দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই অধ্যায়ে লে গুইন একই গল্পে একাধিক দৃষ্টিকোণ সার্থকভাবে ব্যবহারের কৌশল দেখান। বিশেষ করে উপন্যাসে অনেক লেখক চরিত্রগুলোর ভাবনা-চিন্তা ফুটিয়ে তোলার জন্য বা আখ্যানকে বহুমুখী করার জন্য ঘন ঘন দৃষ্টিকোণ বদলান। কিন্তু এতে পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারে যদি পরিবর্তনগুলো যথেষ্ট যত্ন নিয়ে না করা হয়।
লে গুইন পরিকল্পিত দৃষ্টিকোণ–পরিবর্তন ও অবিবেচনাহীন “হেড হপিং”-এর মধ্যে পার্থক্য টানেন। পরিকল্পিত পরিবর্তনে সাধারণত দৃশ্য বা অধ্যায় বিচ্ছিন্ন হয় বা স্পষ্ট কোনো বিভাজন চিহ্ন থাকে। বিপরীতে, “হেড হপিং” হলো একই অনুচ্ছেদ বা দৃশ্যের ভেতরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে এক চরিত্রের মনোভাব থেকে আরেক চরিত্রের মনোভাবের মধ্যে লাফানো। এটি পাঠকের কাছে অস্পষ্টতা তৈরি করে।
অন্যদিকে একাধিক দৃষ্টিকোণ সঠিকভাবে ব্যবহার করলে, লেখক গল্পের জগৎকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে পারেন, লুকিয়ে থাকা উদ্দেশ্য উন্মোচন করতে পারেন, বা বিভিন্ন চরিত্রের অনুভূতি ও ঘটনা-দৃষ্টিকে নানা মাত্রায় তুলে আনতে পারেন। শর্ত হলো, প্রতিটি চরিত্রের কণ্ঠস্বর ও অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র হতে হবে।
এই অধ্যায়ের অনুশীলনীতে লেখককে একই দৃশ্য দুজন আলাদা চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে লিখতে বলেন। দুটি ভার্সনেই ছন্দ, ক্লাইম্যাক্স, আবেগ ও আগ্রহ কীভাবে পাল্টে যায়, সেটি অনুভব করার জন্যই এই অনুশীলন।
অধ্যায় ৮: Crowding এবং Leaping
“Crowding এবং Leaping”—এই অধ্যায়ে লে গুইন গল্পের গতি (পেস) ও বিস্তারিত বর্ণনা নিয়ে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা করেন। “ক্রাউডিং” মানে দৃশ্য বা বিবরণে ঘনত্ব তৈরি করা—অর্থাৎ কোনো ঘটনার বা পরিবেশের ছোটখাট বিশদ, অনুভূতি, সংবেদী দিক, চরিত্রদের মানসিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে দেখানো। এটি লেখাকে সমৃদ্ধ করে এবং পাঠককে মুহূর্তটির গভীরে ডুবিয়ে রাখে।
“লিপিং” হচ্ছে একই আখ্যানের ভেতরে সময় বা স্থান অল্প কথায় পেরিয়ে যাওয়া, যেন অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো দীর্ঘ করা না হয়। লেখক দৃশ্যত সময়ে ‘ঝাঁপ’ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় ঘটনা এড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য বা মুহূর্তে চলে যান। লে গুইন দেখান, গল্পে দুটো পদ্ধতিই দরকারি। কোনো গল্প যদি সর্বদা অতিমাত্রায় বর্ণনার ঘনত্বে ডুবে থাকে, পাঠক ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন। আর যদি সর্বদা লিপিং করেই চলে, তখন গল্প ভগ্নাংশের মতো লাগতে পারে, সংযুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়।
উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখান কীভাবে কোনো বিখ্যাত লেখক কোনো বিশেষ মুহূর্তে দারুণভাবে বর্ণনা এনে নাটকীয়তা ও আবেগ তৈরি করেন, তারপর সময় বা স্থান দ্রুত অতিক্রম করে মূল কাহিনির ধারায় ফিরে যান। এটি পাঠককে গল্পে ডুবে যেতে দেয়, আবার অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো এড়িয়েও যায়।
এই অধ্যায়ের অনুশীলনীতে লেখককে একটি দৃশ্য লিখতে বলেন—প্রথমে সেটাকে “ক্রাউডিং” করে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে, তারপর “লিপিং” করে সময় বা স্থান দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে। এভাবে অনুশীলনে বোঝা যায় কোন অংশকে বিস্তারিত করা দরকার, আর কোন অংশ সংক্ষিপ্তভাবে সম্পন্ন করা যায়।
অধ্যায় ৯: পরোক্ষ বর্ণনা, বা কীভাবে ‘টেল’ করতে হয়
অধ্যায় ৯-এ লে গুইন গদ্যে দৃশ্যায়ন (showing) ও বর্ণনা (telling)-এর মধ্যে যে প্রচলিত দ্বৈরথ রয়েছে, তা নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন। লেখালেখির অনেক পরামর্শক বলেন “Show, don’t tell”—অর্থাৎ সবকিছু যেন অবিকল দৃশ্যায়ন করা হয়। কিন্তু লে গুইন যুক্তি দেন যে, এটি খুব সরলীকৃত নির্দেশনা। সবকিছুকে সর্বদা দেখানোর দরকার নেই—কিছু কিছু ক্ষেত্রে “টেল” বা সারসংক্ষেপে ঘটনাবলি প্রকাশ করাই বেশি কার্যকর।
উদাহরণস্বরূপ, কোনো দীর্ঘ যাত্রাপথের সময় যদি উল্লেখযোগ্য কিছু না ঘটে, তখন তা উপন্যাসে সম্পূর্ণ দৃশ্যাকারে উপস্থাপন করা অর্থহীন। সংক্ষিপ্তভাবে “দুই সপ্তাহের পথ পেরোল ও কয়েকটি শহর অতিক্রম করল” বললেই যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু যদি এই যাত্রা চরিত্রের মানসিক পরিবর্তন বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কারণ হয়, তখন সেই অংশকে show করতে হবে, যাতে পাঠকও সেই অভিজ্ঞতা পায়।
লে গুইন বলেন, পরোক্ষ বর্ণনা বা টেলিং-ও শিল্পের অংশ হতে পারে। একজন বর্ণনাকারী যদি দর্শনীয় বা কবিত্বময় ভঙ্গিতে সারসংক্ষেপ করেন, সেটিও হতে পারে পাঠককে মুগ্ধ করার উপায়। মূল হলো কোথায় সম্পূর্ণ দৃশ্যায়ন প্রয়োজন আর কোথায় সংক্ষেপে বর্ণনা করলেই চলে—এটি নির্বাচনের সক্ষমতা।
তিনি অনুশীলনে লেখকদেরকে একই ঘটনা প্রথমে সরাসরি (show) দৃশ্যায়ন করতে এবং পরে সংক্ষিপ্তভাবে (tell) উপস্থাপন করতে বলেন। এভাবে অনুধাবন করা যায়, কোন ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি কার্যকর বা উপযুক্ত হতে পারে।
অধ্যায় ১০: অনুশীলন, সংশোধন ও লেখকসমাজ
বইয়ের সমাপ্তি ঘটে অনুশীলন, পুনর্লিখন (রিভিশন) ও সম্প্রদায়—এই তিনটি বিষয়ের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে। লে গুইন জোর দিয়ে বলেন, লেখার কারিগরি দক্ষতা শুধু নীতিমালা জেনে অর্জন করা যায় না; এর জন্য ক্রমাগত চর্চা দরকার। শেষ অধ্যায়ে তিনি পুরো বইতে দেওয়া অনুশীলনগুলোর সারাংশ টেনে এনে লেখকদের কেবল একবারের জন্য নয়, নিয়মিতভাবে এই অনুশীলন করার পরামর্শ দেন।
- অনুশীলনকে খেলাধুলা হিসেবে দেখুন: লে গুইন লেখকদের বলেন, ব্যাকরণ বা ধ্বনি নিয়ে গবেষণামূলক অনুশীলন যেন খেলাধুলার আনন্দ নিয়ে করা হয়। বিভিন্ন রীতি ও কৌশল পরীক্ষামূলকভাবে করে দেখতে হবে। কোনো সময়ে সৃষ্টিশীলতা স্থবির মনে হলে, এই সমস্ত অনুশীলন লেখা শুরু করার আগে বা থেমে যাওয়া স্রোত ফের চালু করতে সাহায্য করতে পারে।
- পুনর্লিখন (Revision) হলো শিল্প: তিনি স্পষ্ট করে দেন, পুনর্লিখন বা সম্পাদনা লেখালেখির প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংশ। লেখাকে উন্নত করতে কখনও নির্দয়ভাবে সম্পাদনা করতে হতে পারে—অপ্রয়োজনীয় শব্দ, বাক্য বা কখনও গোটা অধ্যায় বাদও দিতে হতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত সম্পাদনা যেন লেখার প্রাণশক্তিকে ধ্বংস না করে ফেলে। দক্ষ পুনর্লিখন মানে লেখার প্রতি সমান্তরালভাবে সমালোচনামূলক ও সৃষ্টিশীল মনোভাব বজায় রাখা।
- ওয়ার্কশপ ও লেখক–সমাজ: আপডেটেড সংস্করণে লে গুইন লেখালেখির ওয়ার্কশপ, গ্রুপ বা অনলাইন সম্প্রদায় প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন। এইসব গোষ্ঠী লেখালেখি নিয়ে আলোচনার জায়গা, গঠনমূলক সমালোচনার জায়গা—কিন্তু কখনও কখনও সঠিক দিকনির্দেশনা না থাকলে বা ব্যক্তিগত রুচির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে সৃষ্টিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করতেও পারে। তাই তিনি পরামর্শ দেন, লেখককে সব মতামত যাচাই করে নিজের লেখার প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ-বর্জন করতে জানতে হবে।
- অবিরাম যাত্রা: শেষ পর্যন্ত লে গুইন স্মরণ করিয়ে দেন, লেখালেখি হলো এক দীর্ঘ যাত্রা, যার শেষ নেই। বাক্যগঠনের কৌশল শিখে নেওয়া, শব্দের সুর আর ছন্দে দক্ষ হওয়া—সবই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়। আবার প্রতিটি নতুন গল্প বা উপন্যাসও আলাদা চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ নিয়ে আসে। তিনি তাঁর বইয়ের নামের অনুষঙ্গে ফিরে গিয়ে বলেন, সমুদ্রপথের মতোই গল্পের সমুদ্রে পথচলা কখনও একঘেয়ে হয় না; লেখককে স্রোত ও বাতাসের (ভাষা ও পাঠকপ্রত্যাশার) সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়।
এভাবে বইয়ের শেষ অধ্যায়ে লে গুইন লেখকদের আবারও উৎসাহ দেন: অনুশীলন চালিয়ে যাও, নতুন কিছুতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর, ও লেখালেখির বিস্তৃত সম্ভাবনাকে গ্রহণ কর। গল্পের সমুদ্র আসলে সীমাহীন, আর ডাঙায় ফিরে আসার আগ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন বা নাবিকের মতো করে ভ্রমণ চালিয়ে যেতে হবে।
উরসুলা কে. লে গুইনের Steering the Craft শিল্প ও অনুপ্রেরণার মধ্যে একটি সংবেদনশীল ভারসাম্য রচনা করে। এখানে লেখার ধ্বনি ও সুর, বিরামচিহ্নের সূক্ষ্মতা, বাক্যদৈর্ঘ্যের বৈচিত্র, পুনরাবৃত্তির ক্ষমতা, দৃষ্টিকোণ ও সময়ের দক্ষ নিয়ন্ত্রণ—সবই গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে এটি নিছক শৈলীর কৌশল নির্ধারণের তালিকা হয়ে ওঠেনি; বরং লে গুইন লেখালেখির অভিজ্ঞতার ওপর জোর দিয়েছেন, যেখানে লেখার যাপিত রহস্য ও আনন্দ অক্ষুণ্ণ রাখা হয়।
সার্বিকভাবে বইটির কেন্দ্রীয় বার্তা হলো শোনা—শব্দের সঙ্গীত, পাঠকের প্রতিক্রিয়া, নিজের অন্তর্চেতনায় বেজে ওঠা সংশয় ও উদ্দীপনা। লেখক হলেন সৃষ্টির সাথে অভ্যন্তরীণ একাত্মতার অনুসন্ধানকারী। এখানে ভুলত্রুটি পাপ নয়; বরং সেগুলো নিয়ে নিরন্তর চর্চা করে কারিগরি ও সৃজনশীলতার সংগমে আরও পরিশীলিত লেখা সম্ভব।
এ ছাড়া, Steering the Craft-এ লে গুইন দৃষ্টিকোণ ও কণ্ঠস্বরের প্রসঙ্গকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, দেখিয়েছেন গল্প কে বলছে, কেন বলছে, কীভাবে বলছে—এসবই আখ্যানের শক্তি ও আবেদন নির্ধারণ করে। বইটিতে এমন কোনো অতি সরল সিদ্ধান্ত নেই যে, এই রীতিই একমাত্র ঠিক। বরং, প্রতিটি গল্প তার নিজস্ব ছাঁচে ঢালাই হতে চায়, আর লেখককে সেই ছাঁচ সঠিকভাবে ধারণ করতে জানতে হয়।
অনেক লেখালেখির নির্দেশিকায় বাজার ও পণ্যের দিক গুরুত্ব পায়; কিন্তু লে গুইন বরাবরই ভাষার রূপ–রস ও লেখকের নৈতিক-সৃজনশীল দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি লেখাকে যেভাবে অন্বেষণ ও অভিযাত্রা হিসেবে দেখান, তা মনে করিয়ে দেয়, একজন দক্ষ নাবিকের মতোই লেখককে বাতাস, স্রোত, ঢেউ—সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয় এবং প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শেখার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হয়।
সবশেষে, Steering the Craft বইটি লে গুইনের বৃহত্তর সাহিত্যিক পরিচয়ের প্রতিফলন: তাঁর কল্পনাপ্রবণতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। তাঁর মূল জোর অনুশীলনে—নিয়মিত ও সুচিন্তিত অনুশীলন ছাড়া কেউ কখনও ভালো লেখক হতে পারে না। তিনি দেখিয়েছেন, লেখার প্রতিটি স্তরেই চর্চা-পরীক্ষা-ভুল-সংশোধন যুক্ত। গল্পের সমুদ্র যেমন অন্তহীন, তেমনি ভাষার জগৎও অফুরন্ত।
বইটি আমাদের একভাবে বলে যে লেখক একই সঙ্গে একজন দক্ষ কারিগর ও স্বাপ্নিক শিল্পী, একজন সতর্ক শ্রোতা ও নিবিড় ভাষাশিল্পী। শেখার এই প্রক্রিয়া সারা জীবন ধরে চলে, এবং লেখক চাইলেই প্রতিটি গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারেন। সমুদ্রের মতো বিশালতা এবং অজানার সম্ভাবনা নিয়েই লেখালেখির যাত্রা, যেখানে সঠিকভাবে হাল ধরা শিখে নিতে পারলে সেই লেখনীর ভ্রমণ হতে পারে রোমাঞ্চকর ও ফলপ্রসূ।